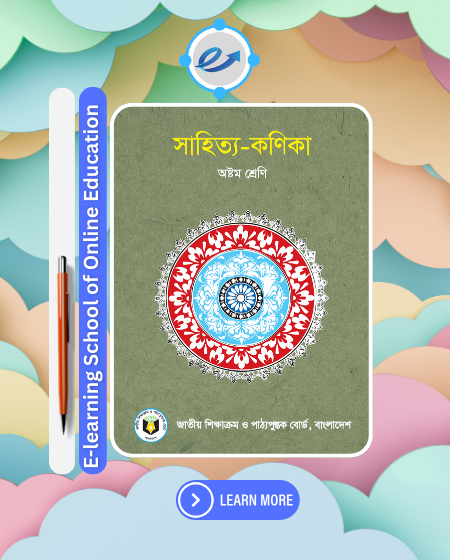অষ্টম শ্রেণির শিক্ষা হলো জুনিয়র পর্যায়ের শেষ ধাপ, যা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি মোড় পরিবর্তনের সময়। এই শ্রেণিতে পাঠ্যসূচি আরও বিস্তৃত ও চ্যালেঞ্জিং হয়, এবং বছরের শেষে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (JSC) বা জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (JDC) পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়। বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT), কৃষি/গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে পাঠদান করা হয়। অষ্টম শ্রেণি শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, সমস্যার সমাধান, বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা ও পরীক্ষামুখী প্রস্তুতির ক্ষমতা গড়ে ওঠে।
e-Learning School (www.e-learningschool.com) এ অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে একটি উন্নত, প্রযুক্তিনির্ভর ও একীভূত শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। এখানে প্রতিটি বিষয়ের জন্য ভিডিও ক্লাস, অধ্যায়ভিত্তিক সাজেশন, অনলাইন কুইজ, মডেল টেস্ট, ও জেএসসি পরীক্ষামুখী প্রস্তুতির জন্য বিশেষ কোর্স উপস্থাপন করা হয়েছে। ২৪/৭ সময়ে শেখার সুযোগ এবং শিক্ষার্থী বান্ধব ডিজাইন এই প্ল্যাটফর্মটিকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য একটি কার্যকর ও উপযোগী শিক্ষার মাধ্যম করে তুলেছে।
চিকিৎসকের আদেশে দেওঘরে এসেছিলাম বায়ু পরিবর্তনের জন্যে। প্রাচীর ঘেরা বাগানের মধ্যে একটা বড় বাড়িতে থাকি । রাত্রি তিনটে থেকে কাছে কোথাও একজন গলাভাঙা একঘেয়ে সুরে ভজন শুরু করে, ঘুম ভেঙে যায়, দোর খুলে বারান্দায় এসে বসি। ধীরে ধীরে রাত্রি শেষ হয়ে আসে— পাখিদের আনাগোনা শুরু হয়। দেখতাম ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভোরে ওঠে দোয়েল। অন্ধকার শেষ না হতেই তাদের গান আরম্ভ হয়, তারপরে একটি দুটি করে আসতে থাকে বুলবুলি, শ্যামা, শালিক, টুনটুনি— পাশের বাড়ির আমগাছে, এ বাড়ির বকুল-কুঞ্জে, পথের ধারের অশ্বত্থগাছের মাথায়— সকলকে চোখে দেখতে পেতাম না, কিন্তু প্রতিদিন ডাক শোনার অভ্যাসে মনে হতো যেন ওদের প্রত্যেককেই চিনি। হলদে রঙের একজোড়া বেনে-বৌ পাখি একটু দেরি করে আসত। প্রাচীরের ধারের ইউক্যালিপটাস গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালটায় বসে তারা প্রত্যহ হাজিরা হেঁকে যেত। হঠাৎ কী জানি কেন দিন-দুই এলো না দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, কেউ ধরলে না তো? এদেশে ব্যাধের অভাব নেই, পাখি চালান দেওয়াই তাদের ব্যবসা— কিন্তু তিন দিনের দিন আবার দুটিকে ফিরে আসতে দেখে মনে হলো যেন সত্যিকার একটা ভাবনা ঘুচে গেল ।
এমনি করে সকাল কাটে। বিকালে গেটের বাইরে পথের ধারে এসে বসি। নিজের সামর্থ্য নেই বেড়াবার, যাদের আছে তাদের প্রতি চেয়ে চেয়ে দেখি। দেখতাম মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে পীড়িতদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই ঢের বেশি। প্রথমেই যেত পা ফুলো ফুলো অল্পবয়সী একদল মেয়ে। বুঝতাম এরা বেরিবেরির আসামি। ফোলা পায়ের লজ্জা ঢাকতে বেচারাদের কত না যত্ন। মোজা পরার দিন নয়, গরম পড়েছে, তবু দেখি কারও পায়ে আঁট করে মোজা পরা। কেউ বা দেখলাম মাটি পর্যন্ত লুটিয়ে কাপড় পরেছে— সেটা পথ চলার বিঘ্ন, তবু, কৌতূহলী লোকচক্ষু থেকে তারা বিকৃতিটা আড়াল রাখতে চায়। আর সবচেয়ে দুঃখ হতো আমার একটি দরিদ্র ঘরের মেয়েকে দেখে। সে একলা যেত। সঙ্গে আত্মীয়-স্বজন নেই, শুধু তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। বয়স বোধ করি চব্বিশ-পঁচিশ, কিন্তু দেহ যেমন শীর্ণ, মুখ তেমনি পাণ্ডুর— কোথাও যেন এতটুকু রক্ত নেই । শক্তি নেই নিজের দেহটাকে টানবার, তবু সবচেয়ে ছোট ছেলেটি তার কোলে। সে তো আর হাঁটতে পারে না —অথচ, ,ফিরে আসবারও ঠাঁই নেই ? কী ক্লান্তই না মেয়েটির চোখের চাহনি । সেদিন সন্ধ্যার তখনও দেরি আছে, দেখি জনকয়েক বৃদ্ধ ব্যক্তি ক্ষুধা হরণের কর্তব্যটা সমাধা করে যথাশক্তি দ্রুতপদেই বাসায় ফিরছেন। সম্ভবত এরা বাতব্যাধিগ্রস্ত, সন্ধ্যার পূর্বেই এদের ঘরে প্রবেশ করা প্রয়োজন । তাঁদের চলন দেখে ভরসা হলো, ভাবলাম যাই, আমিও একটু ঘুরে আসিগে। সেদিন পথে পথে অনেক বেড়ালাম। অন্ধকার হয়ে এলো, ভেবেছিলাম আমি একাকী, হঠাৎ পেছনে চেয়ে দেখি একটি কুকুর আমার পেছনে চলেছে। বললাম, কী রে, যাবি আমার সঙ্গে? অন্ধকার পথটায় বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারবি? সে দূরে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল। বুঝলাম সে রাজি আছে । বললাম, তবে আয় আমার সঙ্গে । পথের ধারের একটা আলোতে দেখতে পেলাম কুকুরটার বয়স হয়েছে; কিন্তু যৌবনে একদিন শক্তিসামর্থ্য ছিল। তাকে অনেক কিছু প্রশ্ন করতে করতে বাড়ির সমুখে এসে পৌঁছলাম। গেট খুলে দিয়ে ডাকলাম, ভেতরে আয়। আজ তুই আমার অতিথি। সে বাইরে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল, কিছুতে ভেতরে ঢোকার ভরসা পেল না। আলো নিয়ে চাকর এসে উপস্থিত হলো, গেট বন্ধ করে দিতে চাইল, বললাম, না, খোলাই থাক । যদি আসে, ওকে খেতে দিস। ঘণ্টাখানেক পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম সে আসে নি— কোথায় চলে গেছে।
পরদিন সকালে বাইরে এসেই দেখি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার সেই কালকের অতিথি। বললাম, কাল তোকে খেতে নেমন্তন্ন করলাম, এলিনে কেন ?
জবাবে সে মুখপানে চেয়ে তেমনি ল্যাজ নাড়তে লাগল। বললাম, আজ তুই খেয়ে যাবি,— না খেয়ে যাসনে বুঝলি? প্রত্যুত্তরে সে শুধু ঘন ঘন ল্যাজ নাড়ল— অর্থ বোধ হয় এই যে, সত্যি বলছো তো?
রাত্রে চাকর এসে জানাল সেই কুকুরটা এসে আজ বাইরের বারান্দার নিচে উঠানে বসে আছে। বামুনঠাকুরকে ডেকে বলে দিলাম, ও আমার অতিথি, ওকে পেট ভরে খেতে দিও ।
পরের দিন খবর পেলাম অতিথি যায় নি। আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে সে আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। বললাম, তা হোক, ওকে তোমরা খেতে দিও ।
আমি জানতাম, প্রত্যহ খাবার তো অনেক ফেলা যায়, এতে কারও আপত্তি হবে না। কিন্তু আপত্তি ছিল এবং অত্যন্ত গুরুতর আপত্তি। আমাদের বাড়তি খাবারের যে প্রবল অংশীদার ছিল এ বাগানের মালির মালিনী— এ আমি জানতাম না। তার বয়স কম, দেখতে ভালো এবং খাওয়া সম্বন্ধে নির্বিকারচিত্ত। চাকরদের দরদ তার পরেই বেশি। অতএব, আমার অতিথি করে উপবাস। বিকালে পথের ধারে গিয়ে বসি, দেখি অতিথি আগে থেকেই বসে আছে ধুলোয়। বেড়াতে বার হলে সে হয় পথের সঙ্গী; জিজ্ঞাসা করি, হ্যাঁ অতিথি, আজ মাংস রান্নাটা কেমন হয়েছিল রে? হাড়গুলো চিবোতে লাগল কেমন? সে জবাব দেয় ল্যাজ নেড়ে, মনে করি মাংসটা তা হলে ওর ভালোই লেগেছে। জানিনে যে মালির বউ তারে মেরেধরে বার করে দিয়েছে— বাগানের মধ্যে ঢুকতে দেয় না, তাই ও সমুখের পথের ধারে বসে কাটায়। আমার চাকরদেরও তাতে সায় ছিল।
হঠাৎ শরীরটা খারাপ হলো, দিন-দুই নিচে নামতে পারলাম না। দুপুরবেলা উপরের ঘরে বিছানায় শুয়ে, খবরের কাগজটা যেইমাত্র পড়া হয়ে গেছে, জানালার মধ্য দিয়ে বাইরের রৌদ্রতপ্ত নীল আকাশের পানে চেয়ে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিলাম। সহসা খোলা দোর দিয়ে সিঁড়ির উপর ছায়া পড়ল কুকুরের। মুখ বাড়িয়ে দেখি অতিথি দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে। দুপুরবেলা চাকরেরা সব ঘুমিয়েছে, ঘর তাদের বন্ধ, এই সুযোগে লুকিয়ে সে একেবারে আমার ঘরের সামনে এসে হাজির। ভাবলাম, দুদিন দেখতে পায় নি, তাই বুঝি আমাকে ও দেখতে এসেছে। ডাকলাম, আয় অতিথি, ঘরে আয়। সে এলো না, সেখানে দাঁড়িয়েই ল্যাজ নাড়তে লাগল । জিজ্ঞাসা করলাম—খাওয়া হয়েছে তো রে? কী খেলি আজ?
হঠাৎ মনে হলো ওর চোখ দুটো যেন ভিজেভিজে, যেন গোপনে আমার কাছে কী একটা নালিশ ও জানাতে চায় । চাকরদের হাঁক দিলাম, ওদের দোর খোলার শব্দেই অতিথি ছুটে পালাল
জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁ রে, কুকুরটাকে আজ খেতে দিয়েছিস?
আজ্ঞে না। মালি-বৌ ওরে তাড়িয়ে দিয়েছে যে ।
আজ তো অনেক খাবার বেঁচেছে, সে সব হলো কী?
মালি-বৌ চেঁচেপুঁছে নিয়ে গেছে।
আমার অতিথিকে ডেকে আনা হলো, আবার সে বারান্দার নিচে উঠানের ধুলোয় পরম নিশ্চিন্তে স্থান করে নিল। মালি-বৌয়ের ভয়টা তার গেছে। বেলা যায়, বিকাল হলে উপরের বারান্দা থেকে দেখি অতিথি এই দিকে চেয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে। বেড়াতে যাবার সময় হলো যে।
শরীর সারলো না, দেওঘর থেকে বিদায় নেবার দিন এসে পড়ল। তবু দিন-দুই দেরি করলাম নানা ছলে । আজ সকাল থেকে জিনিস বাঁধাবাঁধি শুরু হলো, দুপুরের ট্রেন। গেটের বাইরে সার সার গাড়ি এসে দাঁড়াল, মালপত্র বোঝাই দেওয়া চলল। অতিথি মহাব্যস্ত, কুলিদের সঙ্গে ক্রমাগত ছুটোছুটি করে খবরদারি করতে লাগল, কোথাও যেন কিছু খোয়া না যায়। তার উৎসাহই সবচেয়ে বেশি ।
একে একে গাড়িগুলো ছেড়ে দিলে, আমার গাড়িটাও চলতে শুরু করল। স্টেশন দূরে নয়, সেখানে পৌঁছে নামতে গিয়ে দেখি অতিথি দাঁড়িয়ে। কী রে, এখানেও এসেছিস? সে ল্যাজ নেড়ে তার জবাব দিল, কী জানি মানে তার কী! টিকিট কেনা হলো, মালপত্র তোলা হলো, ট্রেন ছাড়তে আর এক মিনিট দেরি। সঙ্গে যারা তুলে দিতে এসেছিল তারা বকশিশ পেল সবাই, পেল না কেবল অতিথি। গরম বাতাসে ধুলো উড়িয়ে সামনেটা আচ্ছন্ন করেছে, যাবার আগে তারই মধ্য দিয়ে ঝাপসা দেখতে পেলাম— স্টেশনের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে অতিথি । ট্রেন ছেড়ে দিলে, বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না। কেবলই মনে হতে লাগল, অতিথি আজ ফিরে গেয়ে দেখবে বাড়ির লোহার গেট বন্ধ, ঢুকবার জো নেই! পথে দাঁড়িয়ে দিন-দুই তার কাটবে, হয়তো নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের কোনো ফাঁকে লুকিয়ে উপরে উঠে খুঁজে দেখবে আমার ঘরটা। হয়তো, ওর চেয়ে তুচ্ছ জীব শহরে আর নেই, তবু দেওঘরে বাসের কটা দিনের স্মৃতি ওকে মনে করেই লিখে রেখে গেলাম।
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:
"অতিথির স্মৃতি" বিখ্যাত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি অনবদ্য হৃদয়স্পর্শী গদ্যরচনা। এটি লেখকের আত্মজীবনীমূলক অভিজ্ঞতার রূপায়ণ, যেখানে তিনি রোগ থেকে সেরে ওঠার জন্য দেওঘরে অবস্থানকালে একজন নির্বাক অথচ বিশ্বস্ত অতিথি — একটি পথকুকুরের সঙ্গে তার গড়ে ওঠা এক নির্মল সম্পর্কের কথা বলেছেন। এই রচনায় মানবতা, সহানুভূতি ও আত্মিক বন্ধনের গভীর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।
মূল বিষয়বস্তু:
গল্পটি শুরু হয় লেখকের চিকিৎসকের নির্দেশে দেওঘরে বায়ু পরিবর্তনের জন্য আগমন দিয়ে। তিনি একটি প্রাচীরবেষ্টিত বাগানঘেরা বাড়িতে বাস করেন। প্রতিদিন ভোরে পাখির কলতান, বিকালে রোগাক্রান্ত নারীদের চলাফেরা, আর হঠাৎই এক পথকুকুরের সঙ্গে দেখা — এগুলো ধীরে ধীরে লেখকের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।
লেখক কুকুরটিকে "অতিথি" হিসেবে সম্মান দেন। অতিথি তার সঙ্গী হয় বিকালের হাঁটায়, রাতে বাড়ির বাইরে বসে থাকে, সকালে দেখা করতে আসে। একসময় লেখকের অসুস্থতার জন্য দু’দিন দেখা না হওয়ায় অতিথি নিজেই ঘরে এসে উপস্থিত হয়। অথচ বাড়ির মালি-বউ ও কিছু চাকরের নিষ্ঠুরতায় সে যথাযথ আদর-যত্ন পায় না।
লেখক যখন দেওঘর ছাড়ার প্রস্তুতি নেন, অতিথির ব্যস্ততা ও আন্তরিক সহযোগিতার চিত্রটি অত্যন্ত আবেগঘন। এমনকি লেখক স্টেশনে পৌঁছানোর পরও অতিথি তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু লেখকের ট্রেন ছেড়ে দেয়, আর পথকুকুর অতিথি ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে — একাকী, বিমর্ষ।
এই শেষ দৃশ্য হৃদয় ছুঁয়ে যায়, যেখানে লেখকের মনে হতে থাকে — সেই অতিথি হয়তো আর কখনো স্বাভাবিকভাবে ফিরে যেতে পারবে না, আবার কেউ তাকে আর সে ভালোবাসা দেবে না। “অতিথির স্মৃতি” গল্পটি ছোট হলেও এর অনুভব ও প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। একজন অসহায় পথকুকুরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক নীরব অথচ গভীর সম্পর্কের গল্প — যা পাঠকের হৃদয়ে মমতা, দায়িত্ববোধ ও দয়া জাগিয়ে তোলে। এটি কেবল একটি কুকুরের গল্প নয়, এটি মানবিকতার এক নীরব আহ্বান।
নাম: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
জন্ম: ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬, দেবানন্দপুর, হুগলি, ব্রিটিশ ভারত (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ)
মৃত্যু: ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮, কলকাতা, ভারত
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী ও উপন্যাসিক। তার রচনায় সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, সমাজের কুপ্রথা, নারীর প্রতি সহানুভূতি এবং মানবিক বোধ গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সহজ-সরল ভাষা, প্রাণবন্ত চরিত্র ও আবেগময় গল্পের মাধ্যমে তিনি অগণিত পাঠকের হৃদয় জয় করেছেন।
নারী-চরিত্র চিত্রণে পারদর্শী: নারীর মানসিক জগত, দুর্দশা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তাঁর লেখায় বারবার উঠে এসেছে।
সামাজিক বাস্তবতা: দারিদ্র্য, সামাজিক কুপ্রথা, অনাদৃত প্রেম, আত্মত্যাগ — তাঁর লেখার প্রধান উপজীব্য।
সহজ ভাষা ও প্রবল আবেগ: সাধারণ মানুষ সহজেই বুঝতে পারে এবং আবেগে ভেসে যেতে পারে।
তার রচনার ওপর বহু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে (যেমন: দেবদাস – বিভিন্ন ভাষায় বারবার তৈরি)
বাংলা সাহিত্য ছাড়াও হিন্দি, ওড়িয়া, তামিলসহ বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে
আজও তিনি বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয়তম লেখকদের একজন
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুধু সাহিত্যিক নন, তিনি বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতির এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।
“অতিথির স্মৃতি”-র মতো ছোট রচনার মধ্যেও তাঁর গভীর মানবতাবোধ ও সংবেদনশীলতা অনন্যভাবে প্রকাশ পায়।
১. লেখক কোথায় এসেছিলেন বায়ু পরিবর্তনের জন্য?
ক) শিলিগুড়ি
খ) কাশী
গ) দেওঘর ✅
ঘ) দার্জিলিং
২. লেখকের প্রাতঃস্মরণীয় পাখিগুলোর মধ্যে কে সবার আগে গান শুরু করত?
ক) শালিক
খ) দোয়েল ✅
গ) বুলবুলি
ঘ) টুনটুনি
৩. হলুদ রঙের বেনেবৌ পাখি কোথায় বসে হাজিরা দিত?
ক) আমগাছে
খ) বকুল গাছে
গ) ইউক্যালিপটাস গাছে ✅
ঘ) অশ্বত্থ গাছে
৪. লেখক যে কুকুরটির কথা বলেছেন, তাকে কী নামে সম্বোধন করেছেন?
ক) কালু
খ) অতিথি ✅
গ) পুসু
ঘ) পাগলা
৫. লেখকের মতে, পায়ে ফোলা মেয়েরা কী রোগে আক্রান্ত ছিল?
ক) যক্ষ্মা
খ) গাউট
গ) কুষ্ঠ
ঘ) বেরিবেরি ✅
৬. কুকুরটি প্রথম লেখকের ঘরে আসতে চায়নি কেন?
ক) অসুস্থ ছিল
খ) ভয় পাচ্ছিল ✅
গ) ব্যস্ত ছিল
ঘ) মালপত্র পাহারা দিচ্ছিল
৭. লেখকের অতিথিকে কে খেতে দিত না?
ক) রাঁধুনি
খ) বামুন ঠাকুর
গ) মালি-বৌ ✅
ঘ) লেখকের বন্ধু
৮. লেখকের যাত্রার দিন অতিথির ব্যবহার কেমন ছিল?
ক) উদাসীন
খ) ঘুমিয়ে ছিল
গ) খবরদারি করছিল ✅
ঘ) বিদায় জানাতে আসেনি
৯. লেখক যখন ট্রেনে উঠলেন, অতিথি তখন কোথায় ছিল?
ক) প্ল্যাটফর্মে
খ) ট্রেনের ভিতরে
গ) লেখকের সঙ্গে
ঘ) স্টেশনের ফটকের বাইরে ✅
১০. "অতিথির স্মৃতি" রচনাটি মূলত কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে রচিত?
ক) ভ্রমণবৃত্তান্ত
খ) প্রেমের গল্প
গ) মানবতা ও প্রাণীর সম্পর্ক ✅
ঘ) রাজনৈতিক আন্দোলন
১১. লেখকের ধারণা অনুযায়ী পাখি চালান দেওয়া কাদের ব্যবসা?
ক) মালির
খ) ব্যাধদের ✅
গ) দারোয়ানের
ঘ) যাত্রীদের
১২. লেখকের ভাষায় “ঘন ঘন ল্যাজ নাড়া”-এর মানে কী ছিল?
ক) না বোঝা
খ) ভয়
গ) সম্মতি ✅
ঘ) ক্লান্তি
১৩. লেখকের অতিথি প্রথম কোথায় বসে থাকত?
ক) বারান্দায়
খ) গেটের বাইরে ✅
গ) ঘরের কোণে
ঘ) মন্দিরের পাশে
১৪. লেখক যে বাড়িতে ছিলেন, তার বাগানে কে কর্তৃত্ব করত?
ক) বাবুর্চি
খ) মালি-বৌ ✅
গ) দারোয়ান
ঘ) বৃদ্ধ রাঁধুনি
১৫. অতিথির প্রতি লেখকের মনোভাব কেমন ছিল?
ক) বিরক্তিকর
খ) তাচ্ছিল্যপূর্ণ
গ) কৌতূহলী
ঘ) স্নেহপূর্ণ ✅
১৬. অতিথি লেখকের সঙ্গে কোথায় কোথায় যেত?
ক) রান্নাঘর
খ) ঘরের ভিতর
গ) সন্ধ্যাবেলায় হাঁটতে ✅
ঘ) বিছানায় শুতে
১৭. অতিথি লেখকের ঘরে কীভাবে ঢুকেছিল?
ক) চাকর ডাকলে
খ) নিজের ইচ্ছায় লুকিয়ে ✅
গ) দারোয়ান নিয়ে এলো
ঘ) খাবারের লোভে
১৮. অতিথি লেখকের অসুস্থতার সময় কী করেছিল?
ক) বাইরে অপেক্ষা করেছিল ✅
খ) ঘরে ঢুকে খাবার খেয়েছিল
গ) উধাও হয়ে গিয়েছিল
ঘ) কারও সঙ্গে ঝগড়া করেছিল
১৯. লেখক অতিথিকে কী নাম দেন?
ক) পোষ্য
খ) অবলা
গ) অতিথি ✅
ঘ) সাথী
২০. লেখকের চোখে অতিথি ছিল কেমন ধরনের কুকুর?
ক) ছোট, দুর্বল
খ) বড়, হিংস্র
গ) বয়স্ক, অভিজ্ঞ ✅
ঘ) ছানা কুকুর
২১. লেখক কী কারণে দুদিন নিচে নামতে পারেননি?
ক) বৃষ্টির কারণে
খ) অসুস্থতার কারণে ✅
গ) কুকুরের ভয়ে
ঘ) গাড়ি নেই
২২. লেখক যখন ট্রেনে ওঠেন, তখন অতিথি কোথায় ছিল?
ক) গাড়ির ভেতর
খ) লেখকের পায়ে
গ) স্টেশনের গেটে ✅
ঘ) বাড়ির বারান্দায়
২৩. লেখকের বাড়িতে অতিথির থাকার বিষয়ে আপত্তি ছিল কার?
ক) মালি-বৌয়ের ✅
খ) লেখকের বন্ধুর
গ) পাড়ার লোকদের
ঘ) বৃদ্ধ দারোয়ানের
২৪. লেখকের ট্রেন ছাড়ার সময় অতিথির কী অবস্থা ছিল?
ক) খুশি
খ) উত্তেজিত
গ) একদৃষ্টে চেয়ে ছিল ✅
ঘ) ঘুমিয়ে পড়েছিল
২৫. লেখকের মতে, “অতিথি” কোথায় সবচেয়ে বেশি অবহেলার শিকার হতো?
ক) মন্দিরে
খ) শহরে ✅
গ) গ্রামে
ঘ) পাহাড়ে
গল্পে লেখক অসুস্থ অবস্থায় বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘরে যান। সেখানে একটি পথকুকুরের সঙ্গে তার হৃদ্যতা গড়ে ওঠে।
ক) ‘বায়ু পরিবর্তন’ বলতে কী বোঝায়?
খ) লেখকের সঙ্গে কুকুরটির সম্পর্ক কেমন ছিল?
গ) লেখকের আচরণ আমাদের কী মূল্যবোধ শেখায়?
ঘ) এই গল্প থেকে পশুপ্রেমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
লেখকের অতিথি একটি পথকুকুর হলেও সে লেখকের জীবনে গভীর ছাপ ফেলেছিল।
ক) অতিথি শব্দের অর্থ লেখো।
খ) কুকুরটি লেখকের জীবনে কী ভূমিকা পালন করেছে?
গ) গল্পের কুকুরটিকে লেখক অতিথি বলে সম্বোধন করলেন কেন? ব্যাখ্যা করো।
ঘ) নিজের পছন্দের কোনো প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লেখো।
গল্পে দেখা যায় লেখকের অতিথিকে খাবার না দিয়ে তাড়িয়ে দেয় মালির বউ।
ক) ‘তাড়িয়ে দেওয়া’ কী ধরনের কাজ?
খ) লেখক কুকুরটির জন্য কী কী করেছেন?
গ) গল্পে মালির বউয়ের আচরণ ও লেখকের আচরণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।
ঘ) পশুদের প্রতি সহানুভূতি না দেখালে সমাজে কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে?
গল্পে লেখক পাখিদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন এবং তাদের চিনতেন ডাকের মাধ্যমে।
ক) দোয়েল কোন শ্রেণির পাখি?
খ) লেখকের পাখিদের প্রতি ভালোবাসা কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে?
গ) পাখিদের পর্যবেক্ষণ লেখকের মানসিক অবস্থায় কী প্রভাব ফেলেছে?
ঘ) প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কতটা গুরুত্বপূর্ণ? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো।
‘অতিথির স্মৃতি’ একটি মানবিক আবেগে পরিপূর্ণ গল্প।
ক) স্মৃতি কাকে বলে?
খ) লেখকের মনে অতিথির প্রতি এত টান কেন জন্মেছিল?
গ) গল্পের শিরোনাম কতটা উপযুক্ত? বিশ্লেষণ করো।
ঘ) অতিথির সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক থেকে তুমি কী শিক্ষাগ্রহণ করলে? ব্যাখ্যা করো।
লেখক দেওঘর ছাড়ার দিন অতিথি স্টেশন পর্যন্ত যায়।
ক) স্টেশন কী?
খ) অতিথির স্টেশনে উপস্থিত থাকার গুরুত্ব কী?
গ) লেখকের মনের অবস্থা ট্রেন ছাড়ার সময় কেমন ছিল? ব্যাখ্যা করো।
ঘ) একবার কল্পনা করে লেখো, যদি অতিথি কথা বলতে পারত, সে লেখককে কী বলত?
গল্পে অতিথি দিনের পর দিন লেখকের সঙ্গেই কাটায়, তবু তাকে কেউ পছন্দ করে না।
ক) 'সঙ্গী' শব্দের অর্থ কী?
খ) লেখকের সঙ্গী হিসেবে অতিথির ভূমিকা কী?
গ) সমাজের অবহেলিত প্রাণীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত? বিশ্লেষণ করো।
ঘ) তুমি কীভাবে অবলা প্রাণীদের সাহায্য করতে চাও? একটি পরিকল্পনা লেখো।
লেখক বলেন, "ওর চেয়ে তুচ্ছ জীব শহরে আর নেই"— এই বাক্যে অতিথির দুঃখ ফুটে উঠেছে।
ক) ‘তুচ্ছ’ শব্দের অর্থ লেখো।
খ) লেখকের এই বক্তব্যের পেছনে কী মানসিকতা কাজ করেছে?
গ) সমাজে ছোট ও অবহেলিতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
ঘ) একজন ‘অতিথি’র গুরুত্ব তুমি কীভাবে উপলব্ধি করো? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো।
গল্পে বারবার ‘ল্যাজ নাড়া’ শব্দবন্ধ এসেছে, যা একটি নির্বাক ভাষার প্রতীক।
ক) নির্বাক ভাষা বলতে কী বোঝায়?
খ) কুকুরের ল্যাজ নাড়ার মাধ্যমে কী বোঝানো হয়েছে?
গ) পশুর আবেগ প্রকাশের মাধ্যম সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও।
ঘ) ভাষা ছাড়াও প্রাণীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার উপায় কী কী হতে পারে?
গল্পের লেখক একজন মানবিক ও সংবেদনশীল ব্যক্তি।
ক) সংবেদনশীল কাকে বলে?
খ) লেখকের সংবেদনশীলতার দুটি উদাহরণ দাও।
গ) একজন সাহিত্যিকের সংবেদনশীলতা তার রচনায় কীভাবে ফুটে ওঠে?
ঘ) তুমি কীভাবে নিজের চারপাশের মানুষের প্রতি সংবেদনশীল হতে পারো? যুক্তি দাও।
১. গল্পের মূলভাব অনুধাবন:
শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে লেখক ও একটি পথকুকুরের মধ্যে গড়ে ওঠা আন্তরিক সম্পর্ক এবং তার মাধ্যমে মানবিকতা, দয়া ও মমত্ববোধ বুঝতে শিখবে।
২. পশুপ্রেম ও সহানুভূতির মূল্য উপলব্ধি:
গল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অবলা প্রাণীদের প্রতি দয়া, সহানুভূতি ও সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে।
৩. সাহিত্যিক ভাষা ও উপস্থাপনার সৌন্দর্য বোঝা:
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহজ-সরল অথচ আবেগঘন ভাষা ও বর্ণনাশৈলী বিশ্লেষণ করতে পারবে।
৪. স্মৃতিচারণধর্মী গদ্যরীতি চেনা:
শিক্ষার্থীরা স্মৃতিচারণমূলক গদ্য রচনার কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবে।
৫. সমাজের অবহেলিত প্রাণীদের প্রতি মনোযোগী হওয়া:
গল্পটি পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ববোধ গড়ে উঠবে।
৬. সহজ ও মনোগ্রাহী ভাষায় ভাব প্রকাশের দক্ষতা অর্জন:
শিক্ষার্থীরা গল্পটি অনুসরণ করে নিজে থেকেও আবেগঘন ও মানবিক গদ্য রচনায় আগ্রহী হতে পারবে।
সারাংশে বলা যায়, মনুষ্যত্ব, মানবিকতা ও প্রাণীর প্রতি দায়িত্ববোধ জাগানো এবং ভাষার সরলতায় গভীর ভাব প্রকাশ অনুধাবন করা।
ভাবে আর কাজে সম্বন্ধটা খুব নিকট বোধ হইলেও আদতে এ-জিনিস দুইটায় কিন্তু আসমান-জমিন তফাৎ। ভাব জিনিসটা হইতেছে পুষ্পবিহীন সৌরভের মতো, একটা অবাস্তব উচ্ছ্বাস মাত্র। তাই বলিয়া কাজ মানে যে সৌরভবিহীন পুষ্প, ইহা যেন কেহ মনে করিয়া না বসেন। কাজ জিনিসটাই ভাবকে রূপ দেয়, ইহা সম্পূর্ণভাবে বস্তুজগতের।
তাই বলিয়া ভাবকে যে আমরা মন্দ বলিতেছি বা নিন্দা করিতেছি, তাহা নহে; ভাব জিনিসটা খুবই ভালো। মানুষকে কব্জায় আনিবার জন্য তাহার সর্বাপেক্ষা কোমল জায়গায় ছোঁওয়া দিয়া তাহাকে মাতাইয়া না তুলিতে পারিলে তাহার দ্বারা কোনো কাজ করানো যায় না, বিশেষ করিয়া আমাদের এই ভাব-পাগলা দেশে। কিন্তু শুধু ভাব লইয়াই থাকিব, লোককে শুধু কথায় মাতাইয়া মশগুল করিয়াই রাখিব, এও একটা মন্ত বদ-খেয়াল। এই ভাবকে কার্যের দাসরূপে নিয়োগ করিতে না পারিলে ভাবের কোনো সার্থকতাই থাকে না। তাহা ছাড়া ভাব দিয়া লোককে মাতাইয়া তুলিয়া যদি সেই সময় গরমাগরম কার্যসিদ্ধি করাইয়া লওয়া না হয়, তাহা হইলে পরে সে ভাবাবেশ কর্পূরের মতো উড়িয়া যায়। অবশ্য, এখানে কার্যসিদ্ধি মানে স্বার্থসিদ্ধি নয়। যিনি ভাবের বাঁশি বাজাইয়া জনসাধারণকে নাচাইবেন, তাঁহাকে নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষি হইতে হইবে । তিনি লোকদিগের সূক্ষ্ম অনুভূতি বা ভাবকে জাগাইয়া তুলিবেন মানুষের কল্যাণের জন্য, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। তাঁহাকে একটা খুব মহত্তর উদ্দেশ্য ও কল্যাণ কামনা লইয়া ভাবের বন্যা বহাইতে হইবে, নতুবা বানভাসির পর পলিপড়ার মতো সাধারণের সমস্ত উৎসাহ ও প্রাণ একেবারে কাদাঢাকা পড়িয়া যাইবে । এই জন্য কেহ কেহ বলেন যে, লোকের কোমল অনুভূতিতে ঘা দেওয়া পাপ। কেননা অনেক সময় অনুপযুক্ততা প্রযুক্ত ইহা হইতে সুফল না ফলিয়া কুফলই ফলে। আগে হইতে সমস্ত কার্যের বন্দোবস্ত করিয়া বা কার্যক্ষেত্র তৈয়ার রাখিয়া তবে লোকদিগকে সোনার কাঠির ছোঁওয়া দিয়া জাগাইয়া তুলিতে হইবে। নতুবা তাহারা যখন জাগিয়া দেখিবে যে, তাহারা অনর্থক জাগিয়াছে, কোনো কার্য করিবার নাই, তখন মহা বিরক্ত হইয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িবে এবং তখন আর জাগাইলেও জাগিবে না। কেননা, তখন যে তাহারা জাগিয়া ঘুমাইবে এবং জাগিয়া ঘুমাইলে তাহাকে কেহই ভুলিতে পারে না। তাহা অপেক্ষা বরং কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভালো, সে-ঘুম ঢোল কাঁসি বাজাইয়া ভাঙানো বিচিত্র নয়।
এ-কথাটা একটা মস্ত সত্যি, তাহা এতদিনে আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি। এই যে সেদিন একটা হুজুগে মাতিয়া হুড়হুড় করিয়া হাজার কতক স্কুল-কলেজের ছাত্রদল বাহির হইয়া আসিল, কই তাহারা তো তাহাদের এই সৎ সঙ্কল্প, এই মহৎ ত্যাগকে স্থায়ীরূপে বরণ করিয়া লইতে পারিল না। কেন এমন হইল? একটা সাময়িক উত্তেজনার মুখে এই ত্যাগের অভিনয় করিতে গিয়া 'স্পিরিট'কে কী বিশ্রী ভাবেই না মুখ ভ্যাঙচানো হইল! যাহারা শুধু ভাবের চোটে না বুঝিয়া না শুনিয়া শুধু একটু নামের জন্য বা বদনামের ভয়ে এমন করিয়া তাহাদের ‘স্পিরিট' বা আত্মার শক্তির পবিত্রতা নষ্ট করিল, তাহারা কি দরকার পড়িলে আবার কাল এমনি করিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিবে? আজ যাহারা মুখে চাদর জড়াইয়া কল্যকার ত্যক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার মুখটি চুন করিয়া ঢুকিল, কাল দেশের সত্যিকার ডাক আসিলে তাহারা কি আর তাহাতে সাড়া দিতে পারিবে? হঠকারিতা করিয়া একবার যে ভোগটা ভুগিল বা ভ্রম করিল, তাহারই অনুশোচনাটা তাহারা কিছুতেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না – বাহিরে যতই কেন লা-পরওয়া ভাব দেখাক না। এখন সত্যিকার ডাক শুনিয়া প্রাণ চাহিলেও সে লজ্জায় তাহাতে আসিয়া যোগদান করিতে পারিবে না। এই রূপে আমরা আমাদের দেশের প্রাণশক্তি এই তরুণদের 'স্পিরিট'টাকে কুব্যবহারে আনিয়া মঙ্গলের নামে দেশের মহা শত্রুতা সাধনই করিতেছি না কি? রাগিবার কথা নয়, এখন ইহা রীতিমতো বিবেচনা-সাপেক্ষ। আমাদের এই আশা-ভরসাস্থল যুবকগণ এত দুর্বল হইল কীরূপে বা এমন কাপুরুষের মতো ব্যবহারই বা করিল কেন? সে কি আমাদেরই দোষে নয়? সাপ লইয়া খেলা করিতে গেলে তাহাকে দস্তুরমতো সাপুড়ে হওয়া চাই, শুধু একটু বাঁশি বাজাইতে পারিলেই চলিবে না। আজ যদি সত্যিকার কর্মী থাকিত দেশে, তাহা হইলে এমন সুবর্ণ সুযোগ মাঝ-মাঠে মারা যাইত না। ত্যাগী অনেক আছেন দেশে, কিন্তু কর্মীর অভাবে বা তথাকথিত কর্মী নামে অভিহিত লোকদের সত্য সাধনার অভাবে তাঁহারা কোনো ভালো কাজে আর কোনো অর্থ দিতে চাহেন না, বা অন্য কোনোরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতেও রাজি নন। কী করিয়া হইবেন? তাঁহারা তাঁহাদের চোখের সামনে দেখিতেছেন যে, কতো লোকের কতো মাথার ঘাম পায়ে ফেলার ধন দেশের নামে, কল্যাণের নামে আদায় করিয়া বাজে লোকে নিজেদের উদর পূর্ণ করিতেছে। যাঁহারা সত্যিকার দেশকর্মী— সে বেচারারা সত্যি কথা স্পষ্টভাবে বলিতে গিয়া এই সব কর্মীর কারচুপিতে পুয়ালচাপা পড়িয়া গিয়াছে। বেচারারা এখন ভালো বলিতে গেলেও এই সব মুখোশ-পরা ত্যাগী মহাপুরুষগণ হট্টগোল বাধাইয়া লোককে সম্পূর্ণ উল্টা বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে একদম খেলো, ঝুটা ইত্যাদি প্রমাণ করিয়া দেন। সহজ জনসাধারণের সরল মন এ-সব না ধরিতে পারার দরুন তাহাদের মন অতি অল্পেই ঐ সত্যিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে বিষাইয়া উঠে। ‘দশচক্রে ভগবান ভূত' কথাটা মস্ত সত্যি কথা ।
তাহা হইলে এখন উপায় কী? এক সহজ উপায় এই যে, এখন হইতে জনসাধারণের বা শিক্ষিত কেন্দ্রের উচিত, ভাবের আবেগে অতিমাত্রায় বিহ্বল হইয়া কাণ্ডাকাণ্ড ভালোমন্দ জ্ঞান হারাইয়া না ফেলা। আমরা বলিব, ভাবের সুরা পান করো ভাই, কিন্তু জ্ঞান হারাইও না। তাহা হইলে তোমার পতন, তোমার দেশের পতন, তোমার ধর্মের পতন, মনুষ্যত্বের পতন! ভাবের দাস হইও না, ভাবকে তোমার দাস করিয়া লও। কর্মে শক্তি আনিবার জন্য ভাব-সাধনা কর। ‘স্পিরিট' বা আত্মার শক্তিকে জাগাইয়া তোল, কিন্তু তাই বলিয়া কর্মকে হারাইও না। অন্ধের মতো কিছু না বুঝিয়া না শুনিয়া ভেড়ার মতো পেছন ধরিয়া চলিও না । নিজের বুদ্ধি, নিজের কর্মশক্তিকে জাগাইয়া তোল। তোমার এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যই দেশকে উন্নতির দিকে, মুক্তির দিকে আগাইয়া লইয়া যাইবে। এ-সব জিনিস ভাব-আবিষ্ট হইয়া চক্ষু বুজিয়া হয় না। কোমর বাঁধিয়া কাৰ্যে নামিয়া পড়িতে হইবে এবং নামিবার পূর্বে ভালো করিয়া বুঝিয়া-সুঝিয়া দেখিয়া লইতে হইবে, ইহার ফল কী। শুধু উদ্মো ষাঁড়ের মতো দেওয়ালের সঙ্গে গা ঘেঁষড়াইয়া নিজের চামড়া তুলিয়া ফেলা হয় মাত্র। দেওয়াল প্রভু কিন্তু দিব্যি দাঁড়াইয়া থাকেন। তোমার বন্ধন ওই সামনের দেওয়ালকে ভাঙিতে হইলে একেবারে তাহার ভিত্তিমূলে শাবল মারিতে হইবে।
আবার বলিতেছি, আর ভাবের ঘরে চুরি করিও না। আগে ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখ। কার্যের সম্ভাবনা-অসম্ভাবনার কথা অগ্রে বিবেচনা করিয়া পরে কার্যে নামিলে তোমার উৎসাহ অনর্থক নষ্ট হইবে না । মনে রাখিও তোমার 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তিকে অন্যের প্ররোচনায় নষ্ট করিতে তোমার কোনো অধিকার নাই। তাহা পাপ মহাপাপ !
পাঠ পরিচিতি
নাম: ভাব ও কাজ
লেখক: কাজী নজরুল ইসলাম
রচনার ধরন: প্রবন্ধ
বিষয়বস্তু: ভাব ও কাজের পারস্পরিক সম্পর্ক, বাস্তবতা, আত্মজাগরণ এবং নৈতিক কর্মদৃষ্টি।
পাঠ পরিচিতি:
“ভাব ও কাজ” প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম আবেগপ্রবণতা বা 'ভাব' এবং তার বাস্তব প্রয়োগ 'কাজ'— এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেছেন। লেখক এখানে আবেগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও কর্মহীন আবেগকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। তিনি সত্যিকার পরিবর্তনের জন্য সুসংগঠিত, যুক্তিনির্ভর এবং আত্মচেতনায় সমৃদ্ধ কর্মের আহ্বান জানিয়েছেন।
সারমর্ম ও সারাংশ
সারমর্ম:
নজরুল এখানে বলেছেন, কেবল আবেগ দিয়ে নয়, পরিকল্পিত ও কার্যকর কাজের মাধ্যমেই সমাজ ও জাতির উন্নয়ন সম্ভব। ভাব থাকা ভালো, তবে সেটিকে কাজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত তার কোনো মূল্য নেই। লেখক আবেগভিত্তিক হঠকারী সিদ্ধান্ত ও আন্দোলনের বিপদ তুলে ধরে আত্মজাগরণ ও বিবেকবান কর্মের ওপর জোর দিয়েছেন।
সারাংশ:
প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, ভাব ও কাজ দেখতে কাছাকাছি হলেও প্রকৃতপক্ষে ভিন্নতর। ভাব যেন পুষ্পবিহীন সৌরভ— অস্পষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী, আর কাজ সেই ভাবকে বাস্তব রূপ দেয়। কেবল আবেগে ভেসে কোনো কাজ নয়; বরং সুপরিকল্পিতভাবে যুক্তি ও উপলব্ধির মাধ্যমে কাজে নামা উচিত। আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে কিছুক্ষণ ত্যাগ দেখিয়ে পরে সরে যাওয়া আত্মার অপব্যবহার। লেখক সতর্ক করেছেন— ভাবের নামে অবিবেচক কর্মকাণ্ডে আত্মিক শক্তি নষ্ট না করে বাস্তব ও স্থায়ী কল্যাণমুখী কাজে প্রয়োগ করতে হবে। তাই প্রয়োজন আত্মিক জাগরণ, কিন্তু তাতে কর্মই হবে লক্ষ্য।
শব্দার্থ ও টীকা
ভাব | অনুভব, আবেগ |
কাজ | বাস্তব কর্ম |
সৌরভ | সুবাস |
উচ্ছ্বাস | উত্তেজনা, প্রবল অনুভূতি |
হুজুগে | অন্ধ উন্মাদনায় মাতাল |
আত্মার শক্তি | মানুষের অন্তর্নিহিত নৈতিক শক্তি |
স্পিরিট | প্রাণশক্তি, চেতনা |
ত্যাগী | ত্যাগ স্বীকারকারী ব্যক্তি |
ঋষি | সাধু, জ্ঞানী মানুষ |
বানভাসি | প্লাবিত অবস্থা |
কাদাঢাকা | হতাশ বা ব্যর্থ |
অনুপযুক্ততা | অযোগ্যতা বা অনুপোযোগিতা |
হট্টগোল | গোলযোগ, চিৎকার |
কারচুপি | প্রতারণা, অসততা |
মুখোশ-পরা | ভানকারী, ছদ্মবেশী |
পলিপড়া | প্লাবনের পর জমে থাকা মৃত্তিকা |
সোনার কাঠির ছোঁওয়া | অলৌকিক জাগরণ বা তাত্ক্ষণিক প্রভাব |
হঠকারিতা | না ভেবে কাজ করা |
স্বার্থসিদ্ধি | নিজের সুবিধা আদায় |
কুব্যবহার | অপব্যবহার |
দশচক্রে ভগবান ভূত | অনেকের চাপে সত্যও মিথ্যা মনে হওয়া |
ভেড়ার মতো | অন্ধ অনুসরণ করা |
শাবল | খননের যন্ত্র |
স্পষ্টভাবে | পরিস্কার করে বলা |
ভাবের ঘরে চুরি | আবেগের ভান করা |
লেখক পরিচিতি
নাম: কাজী নজরুল ইসলাম
জন্ম: ২৪ মে ১৮৯৯, চুরুলিয়া, বর্ধমান, ভারত
মৃত্যু: ২৯ আগস্ট ১৯৭৬, ঢাকা, বাংলাদেশ
পরিচিতি: বিদ্রোহী কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সংগীতজ্ঞ ও জাতীয় কবি (বাংলাদেশ)
লেখক পরিচিতি:
কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন বাংলা সাহিত্যের এক ব্যতিক্রমী প্রতিভা। তাঁর লেখায় বিদ্রোহ, মানবতা, সাম্য এবং সত্যের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ফুটে উঠেছে। তিনি কেবল কবি নয়— একজন সংগীতজ্ঞ, গীতিকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও প্রবন্ধকার। তাঁর লেখায় আবেগের সঙ্গে যুক্তির মিলন ঘটেছে। “ভাব ও কাজ” প্রবন্ধে তাঁর সমাজ সচেতনতা, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনিষ্ঠতা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।
১. “ভাব ও কাজ” প্রবন্ধের রচয়িতা কে?
ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
✅ গ) কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২. ভাব কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?
✅ ক) পুষ্পবিহীন সৌরভ
খ) সৌরভবিহীন পুষ্প
গ) জ্বলন্ত অগ্নি
ঘ) জলহীন নদী
৩. কাজ কিসের প্রতীক?
ক) ভাবের উচ্ছ্বাস
✅ খ) বাস্তবতা ও রূপদান
গ) কল্পনা ও চিন্তা
ঘ) অনুভূতি
৪. লেখক 'ভাব-পাগলা দেশ' বলে কোন দেশকে বোঝান?
✅ ক) ভারত
খ) পাকিস্তান
গ) ইংল্যান্ড
ঘ) বাংলাদেশ
৫. শুধু ভাব থাকলে কী হয় না?
✅ ক) কার্যসিদ্ধি
খ) ভাবনা
গ) চিন্তা
ঘ) অনুভব
৬. লেখক কিসে বিশ্বাস করেন?
✅ ক) ভাব ও কাজের সমন্বয়ে
খ) শুধুই ভাবনায়
গ) আবেগে
ঘ) ভাবনা ছাড়া কাজে
৭. কিসে ভাবাবেশ কর্পূরের মতো উড়ে যায়?
✅ ক) যদি কাজ না হয়
খ) যদি কবিতা না লেখা হয়
গ) যদি লেখা না যায়
ঘ) যদি উপদেশ না দেওয়া হয়
৮. লেখক কাকে ‘ত্যাগী ঋষি’ বলেন?
✅ ক) যিনি নিঃস্বার্থভাবে ভাবকে কাজে রূপ দেন
খ) যিনি কাব্য রচনা করেন
গ) যিনি বক্তৃতা করেন
ঘ) যিনি ধর্ম প্রচার করেন
৯. লেখক কোন কাজকে সমর্থন করেন না?
✅ ক) ভাব দিয়ে লোককে মাতিয়ে রেখে কিছু না করা
খ) চিন্তা করে কাজ করা
গ) দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য ত্যাগ
ঘ) আত্মজাগরণ
১০. লেখকের মতে, ভাব কিসের দাস হওয়া উচিত?
✅ ক) কাজের
খ) আবেগের
গ) চিন্তার
ঘ) কল্পনার
১১. “সোনার কাঠির ছোঁয়া” বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
✅ ক) আবেগ উদ্দীপনার অলৌকিক প্রভাব
খ) সোনা খোঁজার যন্ত্র
গ) ছেলেখেলা
ঘ) দানবীরতা
১২. লেখক কিসে বিরক্ত?
✅ ক) ভাব দেখিয়ে কাজ না করায়
খ) ভাব প্রকাশে
গ) ছাত্রদের ত্যাগে
ঘ) বক্তৃতায়
১৩. “স্পিরিট” শব্দটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?
✅ ক) আত্মার শক্তি
খ) শরাব
গ) আত্মা
ঘ) দেহ
১৪. লেখকের মতে, দেশের “আশা-ভরসাস্থল” কারা?
✅ ক) তরুণ সমাজ
খ) বৃদ্ধ মানুষ
গ) রাজনীতিবিদ
ঘ) ব্যবসায়ী
১৫. লেখক কাকে ‘মুখোশ-পরা ত্যাগী’ বলেন?
✅ ক) ভণ্ড নেতা ও কর্মী
খ) সৎ মানুষ
গ) ত্যাগী শিক্ষক
ঘ) কবি
১৬. “দশচক্রে ভগবান ভূত” — এখানে ‘দশচক্র’ বলতে বোঝানো হয়েছে—
✅ ক) লোকজনের চাপে সত্যের বিকৃতি
খ) দশজন কর্মী
গ) দশটা সুযোগ
ঘ) ভগবানের দেহ
১৭. লেখকের মতে, আবেগে কাজ করলে কী হয়?
✅ ক) কার্য ব্যর্থ হয়
খ) সাফল্য আসে
গ) পুরস্কার মেলে
ঘ) মানুষ খুশি হয়
১৮. লেখকের মতে, যুবকরা কেন দুর্বল হয়ে পড়েছে?
✅ ক) আবেগে ভেসে গিয়ে অন্ধভাবে চলার ফলে
খ) পড়াশোনা কম হওয়ার কারণে
গ) অভিভাবকের কারণে
ঘ) খাদ্যের অভাবে
১৯. লেখক কোন ঘুমকে ভালো বলেছেন?
✅ ক) কুম্ভকর্ণের ঘুম
খ) রাতের ঘুম
গ) দুপুরের ঘুম
ঘ) অলস ঘুম
২০. লেখক সাপ নিয়ে খেলা করার জন্য কী প্রয়োজন বলেছেন?
✅ ক) সাপুড়ে হওয়া
খ) বাঁশি বাজানো
গ) ছিপ ধরা
ঘ) ত্যাগী হওয়া
২১. লেখক আবেগের সঙ্গে কিসে বিশ্বাসী?
✅ ক) কর্মে
খ) কাব্যে
গ) বক্তৃতায়
ঘ) বিলাসে
২২. লেখকের মতে কাকে দাস করা উচিত?
✅ ক) ভাবকে
খ) কাজকে
গ) আবেগকে
ঘ) অন্যকে
২৩. লেখকের মতে অন্ধ অনুকরণ কিসের সমান?
✅ ক) ভেড়ার মতো চলা
খ) সিংহের মতো চলা
গ) পাখির মতো চলা
ঘ) কচ্ছপের মতো চলা
২৪. লেখকের ভাষায় ‘উদ্মো ষাঁড়’ কী বোঝায়?
✅ ক) অন্ধ আবেগে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করা
খ) কর্মঠ ব্যক্তি
গ) সাহসী নেতা
ঘ) শক্তিশালী প্রাণী
২৫. লেখকের মতে, সত্যিকার কর্মী কেমন হওয়া উচিত?
✅ ক) চিন্তাশীল, আত্মজাগ্রত ও কর্মদক্ষ
খ) আবেগপ্রবণ
গ) বক্তা
ঘ) অনুসারী
১. কাজী নজরুল ইসলাম ‘ভাব’ এবং ‘কাজ’ এর মধ্যে পার্থক্য কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন? তোমার ভাষায় লিখো।
২. লেখক কেন শুধু ভাব দিয়ে কাজ করাকে অপরিপক্ব মনে করেছেন? তার কারণগুলো আলোচনা করো।
৩. তুমি কীভাবে ‘ভাবকে কাজের দাস’ করা যায়, তা তোমার বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝাও।
৪. প্রবন্ধের আলোকে একটি সামাজিক সমস্যা বেছে নিয়ে লেখো, যেখানে ভাব আর কাজের অভাব দেখা যায়।
৫. ‘হুজুগে ভেসে চলা’ সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য তোমার নিজের অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত করে ব্যাখ্যা করো।
৬. লেখক ‘ত্যাগী ঋষি’ বলতে কী বুঝিয়েছেন? তোমার কাছে ত্যাগ কী ধরনের হতে পারে?
৭. লেখকের মত অনুসারে, কর্মে যুক্তিবোধ ও পরিকল্পনার গুরুত্ব কেন অপরিহার্য?
৮. ‘অন্ধ অনুকরণ’ ও ‘স্বতন্ত্র চিন্তা’ – এ দুটির মধ্যে তোমার ব্যক্তিগত মতামত কি?
৯. লেখক বলেছেন, “ভাবের দাস হওয়া নয়, ভাবকে দাস করা।” এই উক্তির অর্থ কী?
১০. আজকের তরুণ প্রজন্ম কিভাবে কাজী নজরুলের ‘ভাব ও কাজ’ এর আদর্শ অনুসরণ করতে পারে? তোমার মতামত লিখো।
পাঠের উদ্দেশ্য: “ভাব ও কাজ” – কাজী নজরুল ইসলাম
১. ভাব ও কাজের পার্থক্য অনুধাবন করা:
শিক্ষার্থীরা ‘ভাব’ (আবেগ, প্রেরণা) এবং ‘কাজ’ (বাস্তব প্রয়োগ, কর্ম) এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ও সংযোগ সম্পর্কে গভীরভাবে বুঝতে পারবে।
২. বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন:
কেবল ভাবপ্রবণ না হয়ে যুক্তি, পরিকল্পনা ও বাস্তবতাভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।
৪. ত্যাগ ও কল্যাণবোধের গুরুত্ব বোঝা:
শিক্ষার্থীরা শিখবে—আদর্শ, ত্যাগ ও দেশপ্রেম তখনই ফলপ্রসূ হয়, যখন তা কার্যকর পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয়।
৫. সমাজ সচেতনতা ও নেতৃত্ব গঠনে সহায়ক:
তরুণ প্রজন্মকে না জেনে-না বুঝে আবেগে ভেসে গিয়ে হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে সাবধান করবে এবং নেতৃত্বে যুক্তিবোধের প্রয়োজন বোঝাবে।
৬. নৈতিক ও মানবিক চেতনা জাগানো:
আত্মার শক্তিকে পবিত্র ও সুচিন্তিত কাজে নিয়োজিত রাখার আহ্বান শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলবে।
৭. অন্ধ অনুসরণের বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি:
ভেড়ার পালের মতো না চলার উপদেশ শিক্ষার্থীদের নিজস্ব বিচারবোধ তৈরি করতে উৎসাহিত করবে।
ভাবনাশক্তি ও কর্মক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে একজন বিবেকবান, সচেতন, নৈতিক ও কর্মপ্রবণ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠা।
কালবৈশাখীর সময়টা। আমাদের ছেলেবেলার কথা।
বিধু, সিধু, নিধু, তিনু, বাদল এবং আরও অনেকে দুপুরের বিকট গরমের পর নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছি। বেলা বেশি নেই।
বিধু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে বড়। সে হঠাৎ কান খাড়া করে বললে - ঐ শোন – আমরা কান খাড়া করে শুনবার চেষ্টা করলাম। কিছু শুনতে বা বুঝতে না পেরে বললাম – কী রে? -
বিধু আমদের কথার উত্তর দিলে না। তখনো কান খাড়া করে রয়েছে।
হঠাৎ আবার সে বলে উঠল – ঐ-ঐ-শোন -
আমরও এবার শুনতে পেয়েছি—দূর পশ্চিম-আকাশে ক্ষীণ গুড়গুড় মেঘের আওয়াজ।
নিধু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—ও কিছু না—
বিধু ধমক দিয়ে বলে উঠল—কিছু না মানে? তুই সব বুঝিস কিনা? বৈশাখ মাসে পশ্চিম দিকে ওরকম মেঘ ডাকার মানে তুই কিছু জানিস? ঝড় উঠবে। এখন জলে নামব না। কালবৈশাখী। আমরা সকলে ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি ও কী বলছে। কালবৈশাখীর ঝড় মানেই আম কুড়ানো! বাড়ুয্যেদের
মাঠের বাগানে চাঁপাতলীর আম এ অঞ্চলে বিখ্যাত। মিষ্টি কী! এই সময়ে পাকে। ঝড় উঠলে তার তলায়
ভিড়ও তেমনি। যে আগে গিয়ে পৌঁছতে পারে তারই জয়।
সবাই বললাম— তবে থাক । কিন্তু তখনো রোদ গাছপালার মাথায় দিব্যি রয়েছে। আমাদের অনেকের মনের সন্দেহ তখনো দূর হয়
নি। ঝড়-বৃষ্টির লক্ষণ তো কিছু দেখা যাচ্ছে না; তবে বহু দূরাগত ক্ষীণ মেঘের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে । ওরই ক্ষীণ সূত্র ধরে বোকার মতো চাপাতলীর তলায় যাওয়া কি ঠিক হবে?
বিধু আমাদের সকল সংশয় দূর করে দিলে। যেমন সে চিরকাল আমাদের সকল সংশয় দূর করে এসেছে। সে জানিয়ে দিলে যে, সে নিজে এখুনি চাঁপাতলীর আমতলায় যাচ্ছে, যার ইচ্ছে হবে সে ওর সঙ্গে যেতে পারে । এরপর আর আমাদের সন্দেহ রইল না। আমরা সবাই ওর সঙ্গে চললাম।
অল্পক্ষণ পরেই প্রমাণ হলো, ও আমাদের চেয়ে কত বিজ্ঞ। ভীষণ ঝড় উঠল, কালো মেঘের রাশি উড়ে আসতে লাগল পশ্চিম থেকে । বড় বড় গাছের মাথা ঝড়ের বেগে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল, ধুলোতে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল, একটু পরেই ঠান্ডা হাওয়া বইল, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে পড়তে বড় বড় করে ভীষণ বাদলের বর্ষা নামল ।
বড় বড় আমবাগানের তলাগুলি ততক্ষণে ছেলেমেয়েতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আম ঝরছে শিলাবৃষ্টির মতো; প্রত্যেক ছেলের হাতে এক এক বোঝা আম। আমরাও যথেষ্ট আম কুড়ুলাম, আমের ভারে নুয়ে পড়লাম এক একজন। ভিজতে ভিজতে কেউ অন্য তলায় চলে গেল, কেউ বাড়ি চলে গেল আমের বোঝা নামিয়ে রেখে আসতে। আমি আর বাদল সন্ধ্যার অন্ধকারে নদীর ধারের পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছি। পথে কেউ কোথাও নেই, ছোট-বড় ডালপালা পড়ে পথ ঢেকে গিয়েছে; পাকা নোনাসুদ্ধ নোনাগাছের ডাল কোথা থেকে উড়ে এসে পড়েছে, কাঁটাওয়ালা সাঁইবাবলার ডালে পথ ভর্তি, কাঁটা ফুটবার ভয়ে আমরা ডিঙিয়ে পথ চলছি আধ-অন্ধকারের মধ্যে।
এমন সময় বাদল কী একটা পায়ে বেধে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। আমায় বললে- দ্যাখ তো রে জিনিসটা কী? আমি হাতে তুলে দেখলাম একটি টিনের বাক্স, চাবি বন্ধ। এ ধরনের টিনের বাক্সকে পাড়াগাঁ অঞ্চলে বলে, ডবল টিনের ক্যাশ বাক্স। টাকাকড়ি রাখে পাড়াগাঁয়ে। এ আমরা জানি । বাদল হঠাৎ বড় উত্তেজিত হয়ে পড়ল। বললে—দেখি জিনিসটা?
দ্যাখ তো, চিনিস?
- চিনি, ডবল টিনের ক্যাশ বাক্স।
টাকাকড়ি থাকে।
- তাও জানি।
এখন কী করবি?
সোনার গহনাও থাকতে পারে। ভারী দেখেছিস কেমন?
– তা তো থাকেই। টাকা গহনা আছেই এতে।
টিনের ক্যাশ বাক্স হাতে আমরা দুজনে সেই অন্ধকারে তেঁতুলতলায় বসে পড়লাম। দুজনে এখন কী করা যায় তাই ঠিক করতে হবে এখানে বসে। আম যে প্রিয় বস্তু, এত কষ্ট করে জল ঝড় অগ্রাহ্য করে যা কুড়িয়ে এনেছি, তাও একপাশে অনাদৃত অবস্থায় পড়েই রইল, থলেতে বা দড়ির বোনা গেঁজেতে।
বাদল বললে—কেউ জানে না যে আমরা পেয়েছি—
– তা তো বটেই। কে জানবে আর।
এখন কী করা যায় বল।
বাক্স তো তালাবন্ধ-
– এখুনি ইট দিয়ে ভাঙি যদি বলিস তো—ওঃ না জানি কত কী আছে রে এর মধ্যে। তুই আর আমি দুজনে নেব, আর কেউ না। খুব সন্দেশ খাব। ঝড়ের ঝাপটা আবার এলো। আমরা তেঁতুলগাছের গুঁড়িটার আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। তেঁতুলগাছে ভূত আছে সবাই জানে। কিন্তু ভূতের ভয় আমাদের মন থেকে চলে গিয়েছে। অন্য দিনে আমাদের দুজনের সাধ্য ছিল না এ সময় এ গাছতলায় বসে থাকি।
বাদল বলল—শীতে কেঁপে মরছি। কী করা যাবে বল। বাড়ি কিন্তু নিয়ে যাওয়া হবে না। তাহলে সবাইকে
ভাগ দিতে হবে, সবাই জেনে যাবে। কী করবি?
- আমার মাথায় কিছু আসছে না রে।
— ভাঙি তালা । ইট নিয়ে আসি, তুই থাক এখানে ।
না। তালা ভাঙিসনে। ভাঙলেই তো গেল। অন্যায় কাজ হয় তালা ভাঙলে, ভেবে দ্যাখ। কোনো গরিব লোকের হয়তো। আজ তার কী কষ্ট হচ্ছে, রাতে ঘুম হচ্ছে না। তাকে ফিরিয়ে দেব বাক্সটা ।
বাদল ভেবে বললে—ফেরত দিবি?
- দেব ভাবছি।
- কী করে জানবি কার বাক্স?
চল, সে মতলব বার করতে হবে। অধর্ম করা হবে না।
এক মুহূর্তে দুজনের মনই বদলে গেল। দুজনেই হঠাৎ ধার্মিক হয়ে উঠলাম। বাক্স ফেরত দেয়ার কথা মনে আসতেই আমাদের অদ্ভুত পরিবর্তন হলো। বাক্স নিয়ে জল ঝড়ে ভিজে সন্ধ্যার পর অন্ধকারে বাড়ি চলে এলাম। বাদলদের বাড়ির বিচুলিগাদায় লুকিয়ে রাখা হলো বাক্সটা ।
তারপর আমাদের দলের এক গুপ্ত মিটিং বসল বাদলদের ভাঙা নাটমন্দিরের কোণে। বর্ষার দিন—আকাশ মেঘে মেঘাচ্ছন্ন। ঠান্ডা হাওয়া বইছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম। সেই কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টির পরই বাদলা নেমে গিয়েছে। একটা চাঁপাগাছের ফোটা চাঁপাফুল থেকে বর্ষার হাওয়ার সঙ্গে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। ব্যাঙ ডাকছে নরহরি বোষ্টমের ডোবায়। আমাদের দলের সর্দার বিধুর নির্দেশমতো এ মিটিং বসেছিল। বাক্স ফেরত দিতেই হবে- এ আমাদের প্রথম ও শেষ প্রস্তাব। মিটিং-এ সে প্রস্তাব পেশ করার আগেই মনে মনে আমরা সবাই সেটি মেনেই নিয়েছিলাম। বিধুকে বলা হলো বাক্স ফেরত দেয়া সম্বন্ধে আমরা সকলেই একমত, অতএব এখন উপায় ঠাওরাতে হবে বাক্সের মালিককে খুঁজে বের করার। কারও মাথায় কিছু আসে না। এ নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হলো। যে কেউ এসে বলতে পারে বাক্স আমার। কী করে আমরা প্রকৃত মালিককে খুঁজে বার করব? মস্ত বড় কথা। কোনো মীমাংসাই হয় না ।
অবশেষে বিধু ভেবে ভেবে বললে—মতলব বার করিছি। ঘুড়ির মাপে কাগজ কেটে নিয়ে আয় দিকি। বলেছি—বিধুর হুকুম অমান্য করার সাধ্য আমাদের নেই। দু-তিনখানা কাগজ ঐ মাপে কেটে ওর সামনে হাজির করা হলো ।
বিধু বললে—লেখ—বাদল লিখুক। ওর হাতের লেখা ভালো । বাদল বলল—কী লিখব বলো-
লেখ বড় বড় করে। বড় হাতের লেখার মতো। বুঝলি? আমি বলে দিচ্ছি— - বলো-
আমরা একটা বাক্স কুড়িয়ে পেয়েছি। যার বাক্স তিনি রায়বাড়িতে খোঁজ করুন । ইতি - বিধু, সিধু, নিধু, তিনু। আমি আর বাদল আপত্তি করে বললাম-বারে, আমরা কুড়িয়ে পেলাম, আর আমাদের নাম থাকবে না বুঝি?আমাদের ভালো নাম লেখ ।
বিধু বললে—লিখে দাও । ভালোই তো। ভালো নাম সবারই লেখ ।
তিনখানা কাগজ লিখে নদীর ধারের রাস্তায় ভিন্ন ভিন্ন গাছে বেলের আঠা দিয়ে মেরে দেওয়া হলো।
দু-তিন দিন কেটে গেল ।
কেউ এল না ।
তিন দিন পরে একজন কালোমতো রোগা লোক আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে এসে দাঁড়াল। আমি তখন
সেখানে বসে পড়ছি। বললাম—কী চাও?
– বাবু, ইদিরভীষণ কার নাম?
– আমার নাম। কেন? কী চাই?
একটা বাক্স আপনারা কুড়িয়ে পেয়েছেন?
আমার নামের বিকৃত উচ্চারণ করাতে আমি চটে গিয়েছি তখন। বিরক্তিভাবে বললাম—কী রকম বাক্স
- কাঠের বাক্স ।
- না। যাও।
বাবু, কাঠের নয়, টিনের বাক্স।
– কী রঙের টিন?
- কালো ।
- না। যাও—
- বাবু দাঁড়ান, বলছি । মোর ঠিক মনে হচ্ছে না। এই রাঙা মতো—
– না, তুমি যাও ৷
লোকটা অপ্রতিভভাবে চলে গেল। বিধুকে খবরটা দিতে সে বললে-ওর নয় রে । লোভে পড়ে এসেছে। ওর মতো কত লোক আসবে।
আবার তিন-চার দিন কেটে গেল।
বিধুর কাছে একজন লোক এলো তারপরে । তারও বর্ণনা মিলল না; বিধু তাকে বিদায় দিলে পত্রপাঠ। যাবার সময় সে নাকি শাসিয়ে গেল, চৌকিদারকে বলবে, দেখে নেবে আমাদের ইত্যাদি। বিধু তাচ্ছিল্যের সুরে বললে- যাও যাও, যা পার করো গিয়ে। বাক্স আমরা কুড়িয়ে পাইনি। যাও ।
আর কোনো লোক আসে না ।
বর্ষা পড়ে গেল ভীষণ ।
সেবার আমাদের নদীতে এলো ভীষণ বন্যা ।
বড় বড় গাছ ভেসে যেতে দেখা গেল নদীর স্রোতে। দু-একটা গরুও আমরা দেখলাম ভেসে যেতে। অম্বরপুর চরের কাপালিরা নিরাশ্রয় হয়ে গেল। নদীর চরে ওদের ছোট ছোট ঘরবাড়ি সেবারেও দেখে এসেছি—কী চমৎকার পটলের আবাদ, কুমড়োর খেত, লাউ-কুমড়োর মাচা ওদের চরে! দু পয়সা আয়ও পেত তরকারি বেচে। কোথায় রইল তাদের পটল কুমড়োর আবাদ, কোথায় গেল তাদের বাড়িঘর। আমাদের ঘাটের সামনে দিয়ে কত খড়ের চালাঘর ভেসে যেতে দেখলাম। সবাই বলতে লাগল অম্বরপুর চরের কাপালিরা সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে । একদিন বিকেলে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে একটা লোক এলো। বাবা বসে হাত-বাক্স সামনে নিয়ে জমাজমির হিসেব দেখছেন। গ্রামের ভাদুই কুমোর কুয়ো কাটানোর মজুরি চাইতে এসেছে । আরও দু-একজন প্রজা এসেছে খাজনা পত্তর দিতে। আমরা দু ভাই বাবার কড়া শাসনে বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছি । এমন সময় একটা লোক এসে বললে-দণ্ডবৎ হই, ঠাকুরমশায়।
বাবা বললেন—এসো। কল্যাণ হোক। কোথা থেকে আসা হচ্ছে?
- আজ্ঞে অম্বরপুর থেকে। আমরা কাপালি।
- বোসো। কী মনে করে? তামাক খাও। সাজো।
লোকটা তামাক সেজে খেতে লাগল। সে এসেছে এ গাঁয়ে চাকরির খোঁজে। বন্যায় নিরাশ্রয় হয়ে নির্বিষখোলার গোয়ালাদের চালাঘরে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছে। এই বর্ষায় না আছে কাপড়, না আছে ভাত। দু আড়ি ধান ধার দিয়েছিল গোয়ালারা দয়া করে, সেও এবার ফুরিয়ে এলো । চাকরি না করলে স্ত্রী- পুত্র না খেয়ে মরবে।
বাবা বললেন—আজ এখানে দুটি ডাল-ভাত খেও।
লোকটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—তা খাব। খাচ্ছিই তো আপনাদের। দুরবস্থা যখন শুরু হয় ঠাকুরমশাই, এই গত জষ্টি মাসে নির্বিষখোলার হাট থেকে পটল বেচে ফিরছি; ছোট মেয়েটার বিয়ে দেব বলে গহনা গড়িয়ে আনছিলাম । প্রায় আড়াই শো টাকার গহনা আর পটল-বেচা নগদ টাকা পঞ্চাশটি – একটা টিনের বাক্সের ভেতর ছিল। সেটা যে হাটের থেকে ফিরবার পথে গরুর গাড়ি থেকে কোথায় পড়ে গেল, তার আর খোঁজই হলো না। সেই হলো শুরু—আর তারপর এলো এই বন্যে-
বাবা বললেন—বল কী? অতগুলো টাকা-গহনা হারালে ?
—অদেষ্ট, একেই বলে বাবু অদেষ্ট। আজ সেগুলো হাতে থাকলে— আমি কান খাড়া করে শুনছিলাম। বলে উঠলাম—কী রঙের বাক্স
সবুজ টিনের।
বাবা আমাদের বাক্সের ব্যাপার কিছুই জানেন না। আমায় ধমক দিলেন—তুমি পড়ো না, তোমার সে খোঁজে কী দরকার? কিন্তু আমি ততক্ষণে বইপত্তর ফেলে উঠে পড়েছি। একেবারে এক ছুটে বিধুর বাড়ি গিয়ে হাজির। বিধু আমার কথা শুনে বললে—দাঁড়া, সিধু আর তিনুকেও নিয়ে আসি। ওরা সাক্ষী থাকবে কি না?
বিধুর খুব বুদ্ধি আমাদের মধ্যে। ও বড় হলে উকিল হবে, সবাই বলত।
আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বেশ একটি ছোটখাটো ভিড় জমে গেল। বাক্স ফেরত পেয়ে সে লোকটা যেন কেমন হকচকিয়ে গেল। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কেবল আমাদের মুখের দিকে চায় আর বলে— ঠাকুরমশাই, আপনারা মানুষ না দেবতা? গরিবের ওপর এত দয়া আপনাদের?
বিধু অত সহজে ভুলবার পাত্র নয়। সে বললে- দেখে নাও মাল সব ঠিক আছে কি না আর এই কাকাবাবুর সামনে আমাদের একটা রসিদ লিখে দাও, বুঝলে? কাকাবাবু আপনি একটু কাগজ দিন না ওকে-লিখতে জান তো?
না, ও উকিলই হবে বটে !
আমার বাবা এমন অবাক হয়ে গেলেন ব্যাপার দেখে যে, তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না ।
পরিচিতি:
পাঠের নাম | পড়ে পাওয়া |
লেখক | বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় |
পাঠের ধরন | গল্প |
বিষয়বস্তু | সততা, মানবিকতা ও শৈশবের স্মৃতি |
পাঠ্যের উৎস | বাংলা সাহিত্যের প্রবন্ধ বা ছোটগল্প সংকলন |
মূল থিম / বিষয়বস্তু:
শিক্ষণীয় দিক:
প্রধান চরিত্র:
"পড়ে পাওয়া" গল্পটি শৈশবের সরলতা, উত্তেজনা, ও অন্তর্নিহিত নৈতিক শক্তির এক চমৎকার প্রতিচ্ছবি। বিভূতিভূষণ তার সহজ অথচ গভীর ভাষায় পাঠকদের মনে মানবিকতার বীজ বপন করে দেন।
সারমর্ম:
"পড়ে পাওয়া" গল্পে শৈশবের দুরন্ত স্মৃতি, কালবৈশাখীর আবহ, এবং একটি মূল্যবান টিনের বাক্স কুড়িয়ে পাওয়ার পর সততার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। গল্পটি শিশু চরিত্রদের মানসিক দ্বন্দ্ব, লোভ, অনুশোচনা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে। তারা শেষ পর্যন্ত বাক্সটি প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিয়ে সত্যিকারের নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়।
সারাংশ:
বন্ধুরা নদীতে স্নানে গিয়ে ঝড়ের পূর্বাভাস পেয়ে আম কুড়াতে যায়। ফেরার পথে বাদল ও গল্পকার একটি টিনের বাক্স পায়, যাতে সম্ভবত টাকা ও গহনা ছিল। প্রথমে তারা লোভে পড়ে, কিন্তু পরে বিবেক জাগ্রত হলে বাক্সটি ফেরত দিতে মনস্থ করে। নানা পরিকল্পনার পর তারা প্রকৃত মালিককে শনাক্ত করে বাক্স ফেরত দেয়। গল্পটি সততা ও মানবিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।
শব্দার্থ ও টিকা:
শব্দ | অর্থ |
বিকট | অত্যন্ত তীব্র |
কান খাড়া | মনোযোগসহকারে শোনা |
তাচ্ছিল্য | অবজ্ঞা |
অদৃষ্ট | ভাগ্য |
বিচুলিগাদা | খড়ের গাদা |
জল্পনা-কল্পনা | নানা চিন্তা |
রসিদ | প্রাপ্তির স্বীকৃতিপত্র |
লেখক পরিচিতি:
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪–১৯৫০) বাংলা সাহিত্যের একজন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক। তাঁর লেখায় প্রকৃতির সৌন্দর্য, গ্রামীণ জীবনের চিত্র এবং মানবিক মূল্যবোধ বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। তিনি “পথের পাঁচালী”, “অপরাজিত”, “অরণ্যের দিনরাত্রি” প্রভৃতি উপন্যাস ও অসংখ্য ছোটগল্পের জন্য পরিচিত।
বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ) — ২৫টি:
১. ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের লেখক কে?
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
খ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ✅
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঘ. সুকুমার রায়
২. গল্পের শুরুতে বন্ধুরা কোথায় যায়?
ক. বাগানে
খ. নদীতে ✅
গ. হাটে
ঘ. মাঠে
৩. বিধু কী পূর্বাভাস দেয়?
ক. বৃষ্টি হবে
খ. খেলা হবে
গ. কালবৈশাখী ঝড় আসবে ✅
ঘ. তুষার পড়বে
সৃজনশীল প্রশ্ন
১. "পড়ে পাওয়া" গল্পে বর্ণিত কালবৈশাখীর সময় ও পরিবেশ কেমন ছিল? বিশ্লেষণ করো।
২. গল্পে বিধু চরিত্রটি কেমন? তার বিচক্ষণতার দুটি দৃষ্টান্ত দাও।
৩. গল্পে শিশুদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ও মানবিকতার প্রকাশ কিভাবে ফুটে উঠেছে?
৪. ‘লোভ সংবরণ’ বিষয়টি গল্পে কিভাবে উপস্থাপিত হয়েছে?
৫. তুমি যদি ওই গল্পের চরিত্র হতে, তুমি কী করতে?
পাঠের উদ্দেশ্য
১. গল্প বুঝে পাঠ করা ও বিশ্লেষণ করা শেখা
২. সততা ও নৈতিকতা সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন
3. ভাষা ও শৈলীর সৌন্দর্য অনুধাবন করা
4. চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষমতা অর্জন
5. সৃজনশীল ও বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নে দক্ষতা বৃদ্ধি
6. ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে পাঠের শিক্ষার মিল খুঁজে নেয়া
7. গল্পের মূল্যবোধ জীবনে প্রয়োগ করার অনুপ্রেরণা লাভ
তৈলচিত্রের ভূত
-মানিক বন্দোপাধ্যায়
একদিন সকাল বেলা পরাশর ডাক্তার নিজের প্রকাণ্ড লাইব্রেরিতে বসে চিঠি লিখছিলেন। চোরের মতো নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে নগেন ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তার টেবিল ঘেঁষে দাঁড়াল। পরাশর ডাক্তার মুখ না তুলেই বললেন, 'বোসো, নগেন।'
চিঠিখানা শেষ করে খামে ভরে ঠিকানা লিখে চাকরকে ডেকে সেটি ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে তবে আবার নগেনের দিকে তাকালেন।
‘বসতে বললাম যে! এ রকম চেহারা হয়েছে কেন? অসুখ নাকি ? নগেন ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। চোরকে যেন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সে চুরি করে কি না, এইরকম অতিমাত্রায় বিব্রত হয়ে সে বলল, 'না না, অসুখ নয়, অসুখ আবার কিসের ?
গুরুতর কিছু ঘটেছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে পরাশর ডাক্তার দুহাতের আঙুলের ডগাগুলি একত্র করে নগেনকে দেখতে লাগলেন। মোটাসোটা হাসিখুশি ছেলেটার তেল চকচকে চামড়া পর্যন্ত যেন শুকিয়ে গেছে, মুখে হাসির চিহ্নটুকুও নেই। চাউনি একটু উদভ্রান্ত। কথা বলার ভঙ্গি পর্যন্ত কেমন খাপছাড়া হয়ে গেছে।
নগেন তার মামাবাড়িতে থেকে কলেজে পড়ে। মাস দুই আগে নগেনের মামার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে পরাশর ডাক্তার নগেনকে দেখেছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন কী ঘটেছে যাতে ছেলেটা এরকম বদলে যেতে পারে? ছেলেবেলা থেকে মামাবাড়িতেই সে মানুষ হয়েছে বটে কিন্তু মামার শোকে এরকম কাহিল হয়ে পড়ার মতো আকর্ষণ তো মামার জন্য তার কোনো দিন ছিল না। বড়লোক কৃপণ মামার যে ধরনেরআদর বেচারি চিরকাল পেয়ে এসেছে তাতে মামার পরলোক যাত্রায় তার খুব বেশি দুঃখ হবার কথা নয়। বাইরে মামাকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি দেখালেও মনে মনে নগেন যে তাকে প্রায়ই যমের বাড়ি পাঠাত তাও পরাশর ডাক্তার ভালো করেই জানতেন। পড়ার খরচের জন্য দুশ্চিন্তা হওয়ার কারণও নগেনের নেই, কারণ শেষ সময়ে কী ভেবে তার মামা তার নামে মোটা টাকা উইল করে রেখে গেছেন । নগেন হঠাৎ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'ডাক্তার কাকা, সত্যি করে একটা কথা বলবেন? আমি কি পাগল হয়ে গেছি? পরাশর ডাক্তার একটু হেসে বললেন, 'তোমার মাথা হয়ে গেছ । পাগল হওয়া কি মুখের কথা রে বাবা! পাগল যে হয় অত সহজে সে টের পায় না সে পাগল হয়ে গেছে !’ “
তবে —— দ্বিধা ভরে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ নগেন যেন মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'আচ্ছা ডাক্তার কাকা, প্রেতাত্মা আছে ?'
‘প্রেতাত্মা মানে তো ভূত? নেই।' ‘নেই? তবে –’ অনেকক্ষণ ইতস্তত করে, অনেক ভূমিকা করে, অনেকবার শিউরে উঠে নগেন ধীরে ধীরে আসল ব্যাপারটা খুলে বলল। চমকপ্রদ অবিশ্বাস্য কাহিনি । বিশ্বাস করা শক্ত হলেও পরাশর ডাক্তার বিশ্বাস করলেন। মিথ্যা গল্প বানিয়ে তাকে শোনাবার ছেলে যে নগেন নয়, তিনি তা জানতেন।
মামা তাকেও প্রায় নিজের ছেলেদের সমান টাকাকড়ি দিয়ে গেছেন জেনে প্রথমটা নগেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। মামার এরকম উদারতা সে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে নি। বাইরে যেমন ব্যবহারই করে থাকুন, মামা তাকে নিজের ছেলেদের মতোই ভালোবাসতেন জেনে পরলোকগত মামার জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তিতে তার মন ভরে গেল। আর সেই সঙ্গে জাগল এরকম দেবতার মতো মানুষকে সারা জীবন ভক্তি-ভালোবাসার ভান করে ঠকিয়েছে ভেবে দারুণ লজ্জা আর অনুতাপ। শ্রাদ্ধের দিন অনেক রাত্রে বিছানায় শুতে যাওয়ার পর অনুতাপটা যেন বেড়ে গেল— শুয়ে শুয়ে সে ছটফট করতে লাগল। হঠাৎ এক সময় তার মনে হলো, সারা জীবন তো ভক্তি-শ্রদ্ধার ভান করে মামাকে সে ঠকিয়েছে, এখন যদি সত্য সত্যই ভক্তি-শ্রদ্ধা জেগে থাকে লাইব্রেরি ঘরে মামার তৈলচিত্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে এলে হয়তো আত্মগ্লানি একটু কমবে, মনটা শান্ত হবে।
রাত্রি তখন প্রায় তিনটে বেজে গেছে, সকলে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে, বাড়ি অন্ধকার। এত রাত্রে ঘুমানোর বদলে মামার তৈলচিত্রের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করার জন্য বিছানা ছেড়ে উঠে যাওয়াটা যে রীতিমতো খাপছাড়া ব্যাপার হবে সে জ্ঞান নগেনের ছিল। তাই কাজটা সকালের জন্য স্থগিত রেখে সে ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু তখন তার মাথা গরম হয়ে গেছে। মন একটু শান্ত না হলে যে ঘুম আসবার কোনো সম্ভাবনা নেই, কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করার পর সেটা ভালো করেই টের পেয়ে শেষকালে মরিয়া হয়ে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল ।
লাইব্রেরিটি নগেনের দাদামশায়ের আমলের। লাইব্রেরি সম্পর্কে নগেনের মামার বিশেষ কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তার আমলে গত ত্রিশ বছরের মধ্যে লাইব্রেরির পিছনে একটি পয়সাও খরচ করা হয়েছে কি না সন্দেহ। আলমারি কয়েকটি অল্প দামি আর অনেক দিনের পুরোনো, ভেতরগুলি বেশির ভাগ অদরকারি বাজে বইয়ে ঠাসা এবং ওপরে বহুকালের ছেঁড়া মাসিকপত্র আর নানা রকম ভাঙাচোরা ঘরোয়া জিনিস গাদা করা । টেবিলটি এবং চেয়ার কয়েকটি খুব সম্ভব অন্য ঘর থেকে পেনশন পেয়ে এ ঘরে স্থান পেয়েছে। দেয়ালে তিনটি বড় বড় তৈলচিত্র, সস্তা ফ্রেমে বাঁধানো কয়েকটা সাধারণ রঙিন ছবি ও ফটো টাঙানো। তা ছাড়া কয়েকটা পুরানো ক্যালেন্ডারের ছবিও আছে—কোনোটাতে ডিসেম্বর, কোনোটাতে চৈত্রমাসের বারো তারিখ লেখা কাগজের ফলক এখনো ঝুলছে।
তৈলচিত্রের একটি নগেনের দাদামশায়ের, একটি দিদিমার এবং অপরটি তার মামার। দাদামশায় আর দিদিমার তৈলচিত্র দুটি একদিকের দেয়ালে পাশাপাশি টাঙানো আছে, মামার তৈলচিত্রটি স্থান জুড়ে আছে পাশের দেয়ালের মাঝামাঝি ।
কারো ঘুম ভেঙে যাবে ভয়ে নগেন আলো জ্বালে নি। কিন্তু তাতে তার কোনো অসুবিধা ছিল না, ছেলেবেলা থেকে এ বাড়ির আনাচ-কানাচের সঙ্গে তার পরিচয়। লাইব্রেরিতে ঢুকে অন্ধকারেই সে মামার তৈলচিত্রের কাছে এগিয়ে গেল । অস্ফুট স্বরে ‘আমায় ক্ষমা করো মামা' বলে যেই সে তৈলচিত্রের পায়ের কাছে আন্দাজে স্পর্শ করেছে—বর্ণনার এখানে পৌঁছে নগেন শিউরে চুপ করে গেল। তার মুখ আরও বেশি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, দুচোখ বিস্ফারিত
‘তারপর?’
নগেন ঢোক গিলে জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, 'যেই ছবি ছুঁয়েছি ডাক্তার কাকা, কে যেন আমাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল। সমস্ত শরীর ঝনঝন করে উঠল, তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান হতে দেখি, সকাল হয়ে গেছে, আমি মামার ছবির নিচে মেঝেতে পড়ে আছি ।' পরাশর ডাক্তার গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার আগে কোনো দিন ফিট হয়েছিল নগেন ?’ নগেন মাথা নেড়ে বলল 'ফিট? না, কস্মিনকালেও আমার ফিট হয় নি। আপনি ভুল করেছেন ডাক্তার কাকা, এ ফিট নয়; মরলে তো মানুষ সব জানতে পারে, মামাও জানতে পেরেছেন টাকার লোভে আমি মিথ্যা ভক্তি দেখাতাম। তাই ছবি ছোঁয়ামাত্র রাগে ঘেন্নায় আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন। সবটা শুনুন আগে, তা হলে বুঝতে পারবেন।
সমস্ত সকাল নগেন মড়ার মতো বিছানায় পড়ে রইল। এই চিন্তাটাই কেবল তার মনে ঘুরপাক খেতে লাগল, ভক্তি ভালোবাসার ছলনায় টাকা আদায় করে নিয়েছে বলে পরলোকে গিয়েও তার ওপর মামার এমন জোরালো বিতৃষ্ণা জেগেছে যে তার তৈলচিত্রটি পর্যন্ত তিনি তাকে স্পর্শ করতে দিতে রাজি নন। যাই হোক, নগেন একালের ছেলে, প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পর তার মনে নানারকম দ্বিধা-সন্দেহ জাগতে লাগল। কে জানে রাত্রে যা ঘটেছে তা নিছক স্বপ্ন কিনা। ধৈর্য ধরতে না পেরে দুপুরবেলা সে আবার লাইব্রেরিতে গিয়ে মামার তৈলচিত্র স্পর্শ করে প্রণাম করল। একবার যদি মামা রাগ দেখিয়ে থাকেন, আবার দেখাবেন না কেন? এবার কিছুই ঘটল না। শরীরটা অবশ্য খুব খারাপ হয়ে আছে, মেঝেতে ধাক্কা যেখানে লেগেছিল মাথার সেখানটা ফুলে টনটন করছে এবং সকালে লাইব্রেরিতে মামার তৈলচিত্রের নিচে মেঝেতেই তার জ্ঞান হয়েছিল। কিন্তু এতে বড়জোর প্রমাণ হয়, রাত্রে ঘুমের মধ্যেই হোক আর জাগ্রত অবস্থাতেই হোক লাইব্রেরিতে গিয়ে সে একটা আছাড় খেয়েছিল। নিজের তৈলচিত্রে ভর করে মামাই যে তাকে ধাক্কা দিয়েছিলেন তার কী প্রমাণ আছে? নগেন যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। কিন্তু বেশিক্ষণ তার মনের শাস্তি টিকল না। রাত্রে আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়েই হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, তার তো ভুল হয়েছে ! দিনের বেলা তাকে ধাক্কা দেয়ার ক্ষমতা তো তার মামার এখন নেই, রাত্রি ছাড়া তার মামা তো এখন কিছুই করতে পারেন না! কী সর্বনাশ! তবে তো রাত্রে আরেকবার মামার তৈলচিত্র না ছুঁয়ে কাল রাত্রের ব্যাপারকে স্বপ্ন বলা যায় না ৷ এত রাত্রে আবার লাইব্রেরিতে যাওয়ার কথা ভেবেই নগেনের হৃৎকম্প হতে লাগল। কিন্তু এমন একটা সন্দেহ না মিটিয়েই বা মানুষের চলে কী করে? খানিকটা পরে নগেন আবার লাইব্রেরিতে হাজির । ভয়ে বুক কাঁপছে, ছুটে পালাতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু কী এক অদম্য আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে চলেছে মামার তৈলচিত্রের দিকে। ঘরে ঢুকেই সে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল। মটকার পাঞ্জাবির ওপর দামি শাল গায়ে মামা দেয়ালে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, মুখে একজোড়া মোটা গোঁফ, চোখে ভর্ৎসনার দৃষ্টি। নগেন এগিয়ে গিয়ে মামার পায়ের কাছে ছবি স্পর্শ করল। কেউ তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল না, কিন্তু সমস্ত শরীর হঠাৎ যেন কেমন অস্থির-অস্থির করতে লাগল। তৈলচিত্র থেকে কী যেন তার মধ্যে প্রবেশ করে ভেতর থেকে তাকে কাঁপিয়ে তুলছে।
তবু নগেন যেন বাঁচল। ভয়ের জন্য শরীর এরকম অস্থির অস্থির করতে পারে। সেটা সামান্য ব্যাপার । ফিরে যাওয়ার সময় আলোটা নিভিয়েই নগেন আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার আরেকটা কথা মনে এসেছে। কাল ঘর অন্ধকার ছিল, আজ আলোটা থাকার জন্য যদি মামা কিছু না করে থাকেন? নগেনের ভয় অনেকটা কমে গিয়েছিল, অনেকটা নিশ্চিন্ত মনেই সে অন্ধকারে তৈলচিত্রের কাছে ফিরে গেল। সে জানে অন্ধকারে তৈলচিত্র স্পর্শ করলেও কিছু হবে না। ঘরে একটা আলো জ্বলছে কি জ্বলছে না তাতে বিশেষ কী আসে যায়? ইতস্তত না করেই সে সোজা তৈলচিত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। পরক্ষণে—
“ঠিক প্রথম রাত্রের মতো জোরে ধাক্কা দিয়ে মামা আমায় ফেলে দিলেন ডাক্তার কাকা।'
‘অজ্ঞান হয়ে গেলে ?'
‘না, একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাই নি। অবশ্য আচ্ছন্নের মতো অনেকক্ষণ মেঝেতে পড়েছিলাম, কিন্তু জ্ঞান ছিল। তারপর থেকে আমি ঠিক পাগলের মতো হয়ে গেছি ডাক্তার কাকা। দিনরাত কেবল এই কথাই ভাবি। রোজ কতবার ঠিক করি বাড়ি ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাব, কিন্তু যেতে পারি না, কীসে যেন আমায় জোর করে আটকে রেখেছে।
পরাশর ডাক্তার খানিক্ষণ ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তারপর আর কোনোদিন ছবিটা ছুঁয়েছ?'
“কতবার। দিনে ছুঁয়েছি, রাত্রে ছুঁয়েছি, আলো জ্বেলে ছুঁয়েছি, অন্ধকারে ছুঁয়েছি। ঠিক ওইরকম ব্যাপার ঘটে। দিনে বা রাত্রে আলো জ্বেলে ছুঁলে কিছু হয় না, অন্ধকারে ছোঁয়ামাত্র মামা আমাকে ঠেলে দেন। সমস্ত শরীর যেন ঝনঝনিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে ওঠে। কোনোদিন অজ্ঞান হয়ে যাই, কোনোদিন জ্ঞান থাকে।
বলতে বলতে নগেন যেন একেবারে ভেঙে পড়ল, 'আমি কী করব ডাক্তার কাকা? এমন করে কদিন চলবে?'
পরাশর ডাক্তার বললেন, 'তার দরকার হবে না। আমি সব ঠিক করে দেব। আজ সকলে ঘুমিয়ে পড়লে রাত্রি ঠিক বারোটার সময় তুমি বাইরের ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা কোরো, আমি যাব।'
একটু থেমে আবার বললেন, 'ভূত বলে কিছু নেই, নগেন।
তবু মাঝরাত্রে অন্ধকার লাইব্রেরিতে পরাশর ডাক্তার মৃদু একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এ ঘরে বাড়ির লোক খুব কম আসে। ঘরের বাতাসে পুরোনো কাগজের একটা ভাপসা গন্ধ পাওয়া যায়। নগেন শক্ত করে তার একটা হাত চেপে ধরে কাঁপছে। কীসের ভয়? ভূতের? তৈলচিত্রের ভূতের? ভূতে যে একেবারে বিশ্বাস করে না, যার বদ্ধমূল ধারণা এই যে যত সব অদ্ভূত অথচ সত্য ভূতের গল্প শোনা যায় তার প্রত্যেকটির সাধারণ ও স্বাভাবিক কোনো ব্যাখ্যা আছেই আছে, ছবির ভূতের অসম্ভব আর অবিশ্বাস্য ভূতের ঘরে পা দিয়ে তার কখনো কি ভয় হতে পারে? তবু অস্বস্তি যে বোধ হচ্ছে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। নগেন যে কাহিনি শুনিয়েছে, সারা দিন ভেবেও পরাশর ডাক্তার তার কোনো সঙ্গত ব্যাখ্যা কল্পনা করতে পারেন নি। একদিন নয়, একবার নয়, ব্যাপারটা ঘটেছে অনেকবার। দিনে তৈলচিত্র নিস্তেজ হয়ে থাকে, রাত্রে তার তেজ বাড়ে। কেবল তাই নয়, অন্ধকার না হলে সে তেজ সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না। আরও একটা কথা, রাত্রি বাড়ার সঙ্গে তৈলচিত্র যেন বেশি সজীব হয়ে উঠতে থাকে। প্রথম রাত্রে নগেন অন্ধকারে স্পর্শ করলে ছবি নগেনের হাতটা শুধু ছিটকিয়ে সরিয়ে দিয়েছে, মাঝরাত্রে স্পর্শ করলে এত জোরে তাকে ধাক্কা দিয়েছে যে মেঝেতে আছড়ে পড়ে নগেনের জ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে ।
অশরীরী শক্তি কল্পনা করা ছাড়া এ সমস্তের আর কী মানে হয়?
হয়—নিশ্চয় হয়; মনে মনে নিজেকে ধমক দিয়ে পরাশর ডাক্তার নিজেকে এই কথা শুনিয়ে দিলেন। তারপর চোখ তুলে তাকালেন দেয়ালের যেখানে নগেনের মামার তৈলচিত্রটি ছিল। এ ঘরে তিনি আগেও কয়েকবার এসেছেন, তৈলচিত্রগুলির অবস্থান তার অজানা ছিল না। যা চোখে পড়ল তাতে পরাশর ডাক্তারের বুকটাও ধড়াস করে উঠল। তৈলচিত্রের ওপরের দিকে দুটি উজ্জ্বল চোখ তার দিকে জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে । চোখ দুটির মধ্যে ফাঁক প্রায় দেড় হাত ।
ঠিক এই সময় নগেন ফিসফিস করে বলল, 'আলোটা জ্বালব ডাক্তার কাকা ?'
পরাশর ডাক্তার তার গলার আওয়াজ শুনেই চমকে উঠলেন—‘না।
রাস্তা অথবা পাশের কোনো বাড়ি থেকে সরু একটা আলোর রেখা ঘরের দেয়ালে এসে পড়েছে। তাতে অন্ধকার কমে নি, মনে হচ্ছে যেন সেই আলোটুকুতে ঘরের অন্ধকারটাই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র।
নগেন আবার ফিসফিস করে বলল, 'একটা কথা আপনাকে বলতে ভুলে গেছি ডাক্তার কাকা। দাদামশায় আর দিদিমার ছবি তাঁরা মরবার পর করা হয়েছিল, কিন্তু মামার ছবিটা মরবার আগে মামা নিজে শখ করে
আঁকিয়েছিলেন। হয়তো সেই জন্যেই '
নগেনের শিহরণ স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। ‘ভয় পেয়ে গেছেন ?’
দাঁতে দাঁত লাগিয়ে পরাশর ডাক্তার তৈলচিত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন। কাছাকাছি যেতে জ্বলজ্বলে চোখ দুটির জ্যোতি যেন অনেক কমে গেল। হাত বাড়িয়ে দিতে প্রথমে তার হাত পড়ল দেয়ালে। যত সাহস করেই এগিয়ে এসে থাকুন, প্রথমেই একেবারে নগেনের মামার গায়ে হাত দিতে তার কেমন দ্বিধা বোধ হচ্ছিল। পাশের দিকে হাত সরিয়ে তৈলচিত্রের ফ্রেম স্পর্শ করা মাত্র বৈদ্যুতিক আঘাতে যেন তার শরীরটা ঝনঝন করে উঠল। অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ করে পেছন দিকে দু পা ছিটকে দিয়ে তিনি মেঝেতে বসে পড়লেন ।
পরক্ষণে ভয়ে অর্ধমৃত নগেন আলোর সুইচ টিপে দিল।
মিনিট পাঁচেক পরাশর ডাক্তার চোখ বুজে বসে রইলেন, তারপর চোখ মেলে মিনিট পাঁচেক একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন নগেনের মামার রুপার ফ্রেমে বাঁধানো তৈলচিত্রটির দিকে।
তারপর তীব্র চাপা গলায় তিনি বললেন, 'তুমি একটি আস্ত গর্দভ নগেন।রাগ একটু কমলে পরাশর ডাক্তার বলতে লাগলেন, 'গাধাও তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান। এত কথা বলতে পারলে আমাকে আর এই কথাটা একবার বলতে পারলে না যে তোমার মামার ছবিটা ইতিমধ্যে রুপার ফ্রেমে বাঁধানো হয়েছে আর ছবির সঙ্গে লাগিয়ে দুটো ইলেকট্রিক বাল্ব ফিট করা হয়েছে ?
‘আমি কি জানি! ছ মাস আগে যেমন দেখে গিয়েছিলাম, আমি ভেবেছিলাম ছবিটা এখানে তেমনি অবস্থাতেই আছে।'
“ইলেকট্রিক শক খেয়ে বুঝতে পারো না কীসে শক লাগল, তুমি কোনদেশি ছেলে? আমি তো শক খাওয়া মাত্র টের পেয়ে গিয়েছিলাম তোমার মামার ছবিতে কোনো প্রেতাত্মা ভর করেছেন।
নগেন উদ্ভ্রান্তের মতো বলল, 'রুপার ফ্রেমটা দাদামশায়ের ছবিতে ছিল, চুরি যাবার ভয়ে মামা অনেক দিন আগে সিন্দুকে তুলে রেখেছিলেন। মামার শ্রাদ্ধের দিন মামিমা ফ্রেমটা বার করে মামার ছবিটা বাঁধিয়েছিলেন। আলো দুটো লাগিয়েছে আমার মামাতো ভাই পরেশ ।
'হ্যাঁ। সে এ বছর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে। তাই বলল, এই সামান্য কাজের জন্য ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে পয়সা দেব কেন ?”
পরাশর ডাক্তার একটু হেসে বললেন, ‘পরেশ তোমার মামার উপযুক্ত ছেলেই বটে। কিছু পয়সা বাঁচানোর জন্য বাপের ছবিতে ভূত এনে ছেড়েছে। এ খবরটা যদি আগে দিতে আমায় –
নগেন সংশয়ভরে বলল, 'কিন্তু ডাক্তার কাকা –
পরাশর ডাক্তার রাগ করে বললেন, 'কিন্তু কী? এখনো বুঝতে পারছ না। দিনের বেলা মেন সুইচ অফ করা থাকে, তাই ছবি ছুঁলে কিছু হয় না, ছবি মানে ছবির রুপার ফ্রেমটা। রুপার ফ্রেমটার নিচে কাঠফাট কিছু আছে, দেয়ালের সঙ্গে যোগ নেই, নইলে তোমাদের ইলেকট্রিকের বিল এমন হুহু করে বেড়ে যেত যে আবার কোম্পানির লোককে এসে লিকেজ খুঁজতে হতো। তুমিও আবার ভূতের আসল পরিচয়টা জানতে পারতে । সন্ধ্যার পর বাড়ির সমস্ত আলো জ্বলে আর বিদ্যুৎ তামার তার দিয়ে যাতায়াত করতে বেশি ভালোবাসে কিনা, তাই সে সময় ছবি ছুঁলে তোমার কিছু হয় না। এ ঘরের আলোটা জ্বাললেও তাই হয়। মাঝরাত্রে বাড়ির সমস্ত আলো নিভে যায়, তখন ছবিটা ছুঁলে আর কোনো পথ খোলা নেই দেখে বিদ্যুৎ অগত্যা তোমার মতো বোকা হাবার শরীরটা দিয়েই –'
পরাশর ডাক্তার চুপ করে গেলেন। তার হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, সুযোগ পেলে তার শরীরটা পথ হিসেবে ব্যবহার করতেও বিদ্যুৎ দ্বিধা করে না। তিনি হাঁফ ছাড়লেন। কপাল ভালো তড়িতাহত হয়ে প্রাণে মরতে হয় নি।
পাঠ পরিচিতি
উপাদান | বিবরণ |
পাঠের নাম | তৈলচিত্রের ভূত |
লেখক | মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় |
ধরন | ছোটগল্প (রহস্যভিত্তিক প্রহসন) |
প্রকাশভঙ্গি | কৌতুক ও যুক্তিনির্ভর ঘটনা |
মূল ভাব | যুক্তিবাদ ও আধুনিক বিজ্ঞানের জয় |
বিষয়বস্তু | ভূতের ভয়, কুসংস্কার ও তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা |
সারমর্ম
তৈলচিত্রের ভূত গল্পে কুসংস্কার, ভয় ও যুক্তিবাদকে একসাথে মেলানো হয়েছে। নগেন নামের এক যুবক তার মামার তৈলচিত্রে রাতের বেলায় প্রণাম করতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে আঘাত পায় ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে। বিষয়টি ভূতের ঘটনা মনে হলেও, পরাশর ডাক্তার ঘটনার পেছনের বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজে বের করেন। শেষে জানা যায়, ছবির রুপার ফ্রেমে সংযুক্ত বৈদ্যুতিক তারের কারণে রাতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে শক লাগে। গল্পটি যুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রতি আস্থা জাগায়।
সারাংশ
নগেন তার মামার মৃত্যুর পর অনুতপ্ত হয়ে রাতে লাইব্রেরিতে গিয়ে মামার তৈলচিত্রে প্রণাম করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। এরপর বারবার রাতে অন্ধকারে প্রণাম করতে গিয়ে শারীরিকভাবে কষ্ট পায়। সে ভাবে তার মামার আত্মা রাগ করে তাকে ধাক্কা দেয়। বিষয়টি পরাশর ডাক্তারকে জানালে তিনিও প্রথমে রহস্য বুঝতে পারেন না। পরে গভীর রাতে লাইব্রেরিতে গিয়ে ডাক্তার নিজেই ছবির ফ্রেম স্পর্শ করে শক পান। শেষে বোঝা যায়, ইলেকট্রিক বাল্ব ফিট করার সময় বিদ্যুৎ তার ফ্রেমে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। এতে ভূতের ভয় নয়, একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।
শব্দার্থ ও টিকা
শব্দ/বাক্যাংশ | অর্থ / টীকা |
তৈলচিত্র | তেলরঙে আঁকা ছবি |
উদভ্রান্ত | বিক্ষিপ্ত মনোভাবসম্পন্ন |
ছলনা | প্রতারণা, কৃত্রিমতা |
রুপার ফ্রেম | রুপার তৈরি ছবি ঘেরা কাঠামো |
মেন সুইচ | প্রধান বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ন্ত্রক |
তড়িতাহত | বিদ্যুৎস্পৃষ্ট |
লেখক পরিচিতি: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮–১৯৫৬)
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক। তার রচনায় সমাজবাস্তবতা, মানুষের মানসিক জটিলতা এবং বিজ্ঞানমনস্কতা গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়। বিখ্যাত রচনাগুলোর মধ্যে রয়েছে পদ্মা নদীর মাঝি, পুতুলনাচের ইতিহাস, ও তৈলচিত্রের ভূত।
বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
১. ‘তৈলচিত্রের ভূত’ গল্পের লেখক কে?
ক. বিভূতিভূষণ
খ. শরৎচন্দ্র
গ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ✅
ঘ. সুকান্ত ভট্টাচার্য
২. পরাশর ডাক্তার কে?
ক. নগেনের মামা
খ. বন্ধু
গ. প্রতিবেশী
ঘ. ডাক্তার কাকা ✅
৩. মামার তৈলচিত্রে কী যুক্ত ছিল?
ক. সোনার ফ্রেম
খ. লোহা
গ. রুপার ফ্রেম ও ইলেকট্রিক বাল্ব ✅
ঘ. কাঠের খাঁচা
৪. রাতের বেলায় কী ঘটত নগেনের সাথে?
ক. ভূত দেখত
খ. জ্বর আসত
গ. বিদ্যুৎ শক খেত ✅
ঘ. মামা স্বপ্নে আসতেন
সৃজনশীল প্রশ্ন
১. গল্পে ভূতের ভয়ের পেছনে বিজ্ঞানের কী ব্যাখ্যা পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।
২. পরাশর ডাক্তার চরিত্রটির বিজ্ঞানমনস্কতার দৃষ্টান্ত দাও।
৩. নগেন কেন নিজেকে পাগল ভাবতে থাকে?
৪. গল্পে আলো ও অন্ধকারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।
৫. তৈলচিত্রের ভূত গল্পে কুসংস্কার কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?
৬. নগেনের ভয় ধাপে ধাপে কিভাবে বাড়তে থাকে? ব্যাখ্যা করো।
৭. গল্পের শেষে পরাশর ডাক্তার কীভাবে সত্য উন্মোচন করেন?
৮. ‘ভূত নেই’— লেখকের এই বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো।
৯. শিক্ষার্থীদের জন্য এই গল্প কী শিক্ষাদান করে?
১০. গল্পের শিরোনাম কতটা উপযুক্ত? মতামত দাও।
পাঠের উদ্দেশ্য (পর্যায়ক্রমে)
১. গল্পের কাহিনি ও বিষয়বস্তু অনুধাবন করা
২. বিজ্ঞানের গুরুত্ব ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা
৩. কুসংস্কার ও ভয়ের বাস্তব ব্যাখ্যা খুঁজে বের করার শিক্ষা লাভ
৪. চরিত্র বিশ্লেষণের দক্ষতা অর্জন করা
৫. বিষয়ের ভেতরের গভীর বার্তা বুঝে নেওয়া
৬. সৃজনশীল ও বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নের উত্তর করতে পারা
৭. আধুনিক বিজ্ঞান ও যুক্তিনির্ভর চিন্তাধারার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা
[পূর্বকথা: ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের সামরিক একনায়ক আইয়ুব খান ক্ষমতাচ্যুত হন। এরপর ক্ষমতায় এসে নতুন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। গণতন্ত্রের ধারা অনুসারে পাকিস্তানের শাসনভার পাওয়ার কথা আওয়ামী লীগের অর্থাৎ বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার ও গণতন্ত্র হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ ঢাকায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ডাকেন। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই তিনি হঠাৎ ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন । এই ষড়যন্ত্রমূলক ঘোষণা শুনেই পূর্ব বাংলার সর্বত্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের ঝড় ওঠে। 'জয় বাংলা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা', ‘জাগো জাগো বাঙালি জাগো' ইত্যাদি স্লোগানে শহর-বন্দর-গ্রাম আন্দোলিত হয়। এই পটভূমিতেই ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) প্রায় ১০ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ১৮ মিনিটের ওই ভাষণে তিনি বাঙালির মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান জানান। আবেগে, বক্তব্যে, দিক-নির্দেশনায় এটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে স্বীকৃত। ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর ইউনেস্কো এই ভাষণটিকে “ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব্ দ্য ওয়ার্ল্ড' রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করে।]
ভাইয়েরা আমার,
আজ দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা,রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।
১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন—গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি।
আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসব। আমি বললাম অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব— এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।
ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরও আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম- আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে, যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো ।
ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাব। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।
আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কল কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কী পেলাম আমরা? আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু—আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।
টেলিফোনে আমার সাথে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপর, আমার মানুষের বুকের
উপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে ।
আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কীসের রাউন্ড টেবিল, কার সাথে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সাথে বসবো? হঠাৎ আমার সাথে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন ।
ভাইয়েরা আমার,
২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহিদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন, 'মার্শাল ল' withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না ।
আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে—শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা, কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়—তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু—আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।
আর যে সমস্ত লোক শহিদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো—কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে – নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয় ।
মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেয়ানেয়া চলবে না।
কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Maiores ipsum repellat minus nihil. Labore, delectus, nam dignissimos ea repudiandae minima voluptatum magni pariatur possimus quia accusamus harum facilis corporis animi nisi. Enim, pariatur, impedit quia repellat harum ipsam laboriosam voluptas dicta illum nisi obcaecati reprehenderit quis placeat recusandae tenetur aperiam.
চরিত্র পরিচিতি
নাম বয়স
মোড়ল ৫০
কবিরাজ ৬০
হাসু ৪৫
রহমত ২০
লোক ৪০
(প্রথম দৃশ্য)
[মোড়লের অসুখ । বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে। কবিরাজ মোড়লের নাড়ি পরীক্ষা করছে। মোড়লের আত্মীয় হাসু মিয়া আর মোড়লের বিশ্বাসী চাকর রহমত আলী অসুখ নিয়ে কথা বলছে ।]
হাসু : রহমত, ও রহমত আলী।
হাসু : রহমত, ও রহমত আলী।
হাসু : ভালো করে শোনো, ঐ কবিরাজ যতই নাড়ি দেখুক, তোমার মোড়লের নিস্তার নাই ।
রহমত : অমন ভয় দেখাবেন না। তাহলে আমি হাউমাউ করে কাঁদতে লেগে যাব
হাসু : কাঁদ, মন উজাড় করে কাঁদ। তোমার মোড়ল একটা কঠিন লোক । আমাদের সুবর্ণপুরের মানুষকে বড় জ্বালিয়েছে। এর গরু কেড়ে, তার ধান লুট করে তোমার মোড়ল আজ ধনী। মানুষের কান্না দেখলে হাসে ।
রহমত : আর আজে-বাজে কথা বলবেন না। আপনি বাড়ি যান!
কবিরাজ : এত কোলাহল করো না। আমি রোগীর নাড়ি পরীক্ষা করছি।
রহমত : ও কবিরাজ, নাড়ি কী বলছে! মোড়ল বাঁচবে তো !
কবিরাজ : মূর্খের মতো কথা বল না। মানুষ এবং প্রাণী অমর নয়। আমি যা বলি মনোযোগ দিয়ে তাই শ্রবণ কর ।
হাসু : আমাকে বলুন। মোড়ল আমার মামাতো ভাই ।
রহমত : মোড়ল আমার মনিব ।
কবিরাজ : এই নিষ্ঠুর মোড়লকে যদি বাঁচাতে চাও, তাহলে একটি কঠিন কর্ম করতে হবে।
হাসু বাঘের চোখ আনতে হবে?
কবিরাজ : আরও কঠিন কাজ ।
রহমত : হিমালয় পাহাড় তুলে আনব?
কবিরাজ : পাহাড়, সমুদ্র, চন্দ্র, নক্ষত্র কিছুই আনতে হবে না ৷
মোড়ল : আর সহ্য করতে পারছি না। জ্বলে গেল। হাড় ভেঙে গেল। আমাকে বাঁচাও ।
কবিরাজ : শান্ত হও। ও রহমত, মোড়লের মুখে শরবত ঢেলে দাও।
(রহমত মোড়লকে শরবত দিচ্ছে।)
হাসু : ঐ মোড়ল জোর করে আমার মুরগি জবাই করে খেয়েছে। আমি আজ মুরগির দাম নিয়ে ছাড়ব।
মোড়ল : ভাই হাসু এদিকে এস, আমি সব দিয়ে দেব। আমাকে শান্তি এনে দাও।
কবিরাজ : মোড়ল, তুমি কি আর কোনোদিন মিথ্যা কথা বলবে?
মোড়ল : আর বলব না । এই তোমার মাথায় হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করছি, আর কোনোদিন মানুষের ওপর জবরদস্তি করব না। আমাকে ভালো করে দাও।
কবিরাজ : লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আর কোনোদিন লোভ করবে?
মোড়ল : না । লোভ করব না, অত্যাচার করব না। আমাকে শান্তি দাও। সুখ দাও।
কবিরাজ : তাহলে মনের সুখে শুয়ে থাক, আমি ওষুধের কথা চিন্তা করি।
মোড়ল : সুখ কোথায় পাব? আমাকে সুখ এনে দাও।
হাসু : অন্যের মনে দুঃখ দিলে কোনোদিন সুখ পাবে না ।
মোড়ল : আমার কত টাকা, কত বড় বাড়ি! আমার মনে দুঃখ কেন?
কবিরাজ : চুপ কর। যত কোলাহল করবে তত দুঃখ বাড়বে। হাসু এদিকে এস, আমার কথা শ্রবণ কর ৷ মোড়লের ব্যামো ভালো হতে পারে, যদি...
রহমত : যদি কী?
কবিরাজ : যদি আজ রাত্রির মধ্যেই-
হাসু : কী করতে হবে?
কবিরাজ : যদি একটি ফতুয়া সংগ্রহ করতে পার।
রহমত : ফতুয়া?
কবিরাজ : হ্যাঁ, জামা । এই জামা হবে একজন সুখী মানুষের। তার জামাটা মোড়লের গায়ে দিলে, তৎক্ষণাৎ তার হাড় মড়মড় রোগ ভালো হবে ।
রহমত : এ তো খুব সোজা ওষুধ।
কবিরাজ : সোজা নয়, খুব কঠিন কাজ। যাও, সুখী মানুষকে খুঁজে দেখ । সুখী মানুষের জামা না হলে অসুখী মোড়ল বাঁচবে না।
মোড়ল : আমি বাঁচব । জামা এনে দাও, হাজার টাকা বখশিশ দেব।
(দ্বিতীয় দৃশ্য)
[বনের ধারে অন্ধকার রাত। চাঁদের ম্লান আলো। ছোট একটি কুঁড়েঘরের সামনে হাসু মিয়া ও রহমত গালে হাত দিয়ে ভাবছে।]
রহমত : কী তাজ্জব কথা, পাঁচ গ্রামে একজনও সুখী মানুষ পেলাম না। যাকেই ধরি, সেই বলে, না ভাই, আমি সুখী নই।
হাসু : আর তো সময় নাই ভাই, এখন বারোটা। সুখী মানুষ নাই, সুখী মানুষের জামাও নাই। মোড়ল তো তাহলে এবার মরবে।
রহমত : আহা রে, আমরা এখন কী করব! কোথায় একটা মানুষ পাব, যে কিনা—
হাসু : পাওয়া যাবে না। সুখী মানুষ পাওয়া যাবে না। সুখ বড় কঠিন জিনিস। এ দুনিয়াতে ধনী বলছে, আরও ধন দাও; ভিখারি বলছে, আরও ভিক্ষা দাও; পেটুক বলছে, আরও খাবার দাও । শুধু দাও আর দাও। সবাই অসুখী। কারও সুখ নেই।
রহমত : আমরাও বলছি, মোড়লের জন্য জামা দাও, আমাদের বখশিশ দাও। আমরাও অসুখী।
হাসু : চুপ চুপ! ঘরের মধ্যে কে যেন কথা বলছে।
রহমত : ভূত নাকি? চলেন, পালিয়ে যাই। ধরতে পারলে মাছভাজা করে খাবে।
হাসু : এই যে, ভাই। ঘরের মধ্যে কে কথা বলছ? বেরিয়ে এস।
রহমত : ভূতকে ডাকবেন না ।
[ঘর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এলো ।]
লোক : তোমরা কে ভাই? কী চাও?
হাসু : আমরা খুব দুঃখী মানুষ । তুমি কে?
লোক : আমি একজন সুখী মানুষ।
হাসু : আঁ! তোমার কোনো দুঃখ নাই?
লোক : না। সারা দিন বনে বনে কাঠ কাটি। সেই কাঠ বাজারে বেচি। যা পাই, তাই দিয়ে চাল কিনি, ডাল কিনি। মনের সুখে খেয়ে-দেয়ে গান গাইতে গাইতে শুয়ে পড়ি। এক ঘুমেই রাত কাবার ।
হাসু : বনের মধ্যে একলা ঘরে তোমার ভয় করে না? যদি চোর আসে?
লোক : চোর আমার কী চুরি করবে?
হাসু : তোমার সোনাদানা, জামাজুতা?
(লোকটি প্রাণখোলা হাসি হাসছে)
রহমত : হা হা করে পাগলের মতো হাসছ কেন ভাই!
লোক : তোমাদের কথা শুনে হাসছি। চোরকে তখন বলব, নিয়ে যাও, আমার যা কিছু আছে নিয়ে যাও ।
হাসু : তুমি তাহলে সত্যিই সুখী মানুষ।
লোক : দুনিয়াতে আমার মতো সুখী কে? আমি সুখের রাজা। আমি মস্ত বড় বাদশা ।
রহমত : ও বাদশা ভাই, তোমার গায়ের জামা কোথায়? ঘরের মধ্যে রেখেছ? তোমাকে একশ টাকা দেব। জামাটা নিয়ে এস।
লোক : জামা!
রহমত : জামা মানে জামা! এই যে, আমাদের এই জামার মতো জিনিস। তোমাকে পাঁচশ টাকা দেব। জামাটা নিয়ে এস, মোড়লের খুব কষ্ট হচ্ছে।
লোক : আমার তো কোনো জামা নাই ভাই!
হাসু : মিছে কথা বল না।
লোক : মিছে বলব কেন? আমার ঘরে কিছু নাই। সেই জন্যই তো আমি সুখী মানুষ।
‘আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের এই কথাগুলিতে শিল্পকলার মূল সত্যটি প্রকাশ পেয়েছে। সব মানুষই জীবনের এই আনন্দকে পাওয়ার জন্যে কত রকম চেষ্টা করে যাচ্ছে। আনন্দ প্ৰকাশ জীবনীশক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। আনন্দকে আমরা বুঝি রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ ইত্যাদির সাহায্যে, ইন্দ্রিয়সকলের সাহায্যে। মানুষ যখন আনন্দ পায় তখন সে তার মনকে প্রকাশ করতে চায়—নানা রূপে। তাই সৃষ্টি হলো চিত্রশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, সংগীতশিল্পী, কবি, সাহিত্যিক। পুরাকালের গুহামানুষ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষ নিজের পাওয়া আনন্দকে সুন্দরকে অন্য মানুষের মধ্যে বিস্তার করতে চেয়েছে। তাই সৃষ্টি হয়েছে নানান আঙ্গিকের শিল্পকলা। যেমন- চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নৃত্যকলা, সংগীতকলা, অভিনয়কলা, চলচ্চিত্র, স্থাপত্য ইত্যাদি কলাভঙ্গি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষ তার নিত্য নতুন অবদান রেখে চলেছে শিল্পকলার বিস্তীর্ণ অঙ্গনে শিল্পকলার একটি অস্পষ্ট অর্থ আমরা বুঝতে পারি কিন্তু শিল্পকলার সঠিক অর্থ কী আর শিল্পকলার গুণাগুণ কী, এই প্রশ্ন যদি কেউ করে, তাহলে উত্তর দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন গান শুনে ভালো লাগে, ছবি দেখে ভালো লাগে, কিন্তু ভালো লাগে কেন? এই প্রশ্ন নিয়ে মানুষের মন চিন্তা-ভাবনা করতে লাগল। দেখা গেল, সকল শিল্পকলায় রূপ আছে, ছন্দ আছে, সুর আছে, রং আছে, বিশেষ গড়ন আছে, সবকিছুকে সাজাবার একটি সুবিন্যস্ত নিয়ম আছে। এই নিয়মটি লুকিয়ে থাকে, নিজেকে প্রকাশ করে না, সুন্দরের মধ্যে মিলেমিশে একটা বন্ধন সৃষ্টি করে। নিয়মটি না জানলেও সুন্দরকে চেনা যায়। একটি উপমা দেয়া যাক। পৃথিবীর সব ফুলই একই নিয়ম মেনে ফুল নাম পেয়েছে। আমরা দেখে বলি সুন্দর। এর নিয়মটি হলো, একই বিন্দু থেকে সকল পাপড়ি বিন্দুর চারিদিকে ছড়িয়ে থাকবে। কিন্তু এক নিয়ম মেনেই কত রকম ফুল। নিয়ম মেনেও ফুল স্বাধীনভাবে ফুটে ওঠে। তোমাদের এখন সুন্দরের নিয়ম জানতে হবে না, সুন্দর লাগলেই সুন্দর বলবে। সুন্দর দেখতে দেখতেই একদিন সুন্দরের বিশেষ বিশেষ নিয়মগুলি জানতে পারবে। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, সুন্দরকে জানার যে জ্ঞান তার নাম ‘নন্দনতত্ত্ব'। নন্দনতত্ত্ব মানে সুন্দরকে বিশ্লেষণ করা, সুন্দরকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা। সব সুন্দরের সৃষ্টির মধ্যেই একটা রূপ আছে, তার নাম স্বাধীনতা—অপর নাম যা খুশি ভাই করা। যে কাজ সকলকে আনন্দ দেয় খুশি করে, তাই সুন্দর। স্বার্থপর বা অসংগত আমি-র খুশি নয়, অনেক মনে খুশির বিস্তার করা আমি। অন্ধকার ঘর আলোকিত করবার জন্যে নিয়ম মেনে প্রদীপ জ্বালাতে হয়, ঘরে অসংগত আগুন লাগিয়ে ঘর আলোকিত করা নয়।
আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, কত রকম জিনিস প্রয়োজন হয়—ঘটি, বাটি থেকে বিছানাপত্র। শুধু প্রয়োজন মিটলেই মানুষ খুশি হয় না— মানুষের মন বলে, প্রয়োজন মিটলেই হবে না তাকে সুন্দর হতে হবে। যেমন নকশি কাঁথা, রাত্রে বিছানায় গায়ে দিয়ে শোওয়ার জন্য একটি সামগ্রী – সেটা তো সুন্দর-অসুন্দর হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই প্রয়োজনের জিনিসকে সুঁই আর রঙিন সুতা দিয়ে অপূর্ব নকশা করে সাজিয়েছে গাঁয়ের বধূরা। নকশি কাঁথা দেখলেই সুন্দর লাগে, জিনিসটির প্রয়োজনের কথা মনেই পড়ে না। এ কারণেই সকল জ্ঞানী মানুষ বলেন, সব সুন্দরই সরাসরি প্রয়োজনের বাইরে। প্রয়োজনের কাজ মিটল তো শরীরকে তৃপ্ত করল, আর প্রয়োজনের বাইরে যে সুন্দর তা মনকে তৃপ্ত করল। অর্থাৎ প্রয়োজন আর অপ্রয়োজন মিলিয়েই মানুষের সৌন্দর্যের আশা পূর্ণ হয়।
এবার বিভিন্ন শিল্পকলা নিয়ে সংক্ষিপ্ত করে কিছু বলা যাক। ছবি আঁকা। বিশ্বের সকল দেশেই শিশুরা ছবি আঁকে। বাংলাদেশের ছোটরাও খুব সুন্দর ছবি আঁকতে পারে। ছবি আঁকা মানে 'দেখা শেখা'। ছোটরা প্রকৃতিকে দেখে, মা-বাবা, ভাই-বোন মিলিয়ে একটা সমাজকে দেখে। প্রতিদিনের দেখা বিষয়বস্তু, রং, গড়ন, আকৃতি শিশুমনের কল্পনার সঙ্গে মিলেমিশে যায়। নানা রকম গল্প শুনে, দেশের কথা শুনে, কবিতা ছড়া শুনেও শিশু মনে ছবি তৈরি হতে থাকে। এ সকল দেখা-অদেখা বস্তু নিয়ে শিশুরা ছবি আঁকে কল্পনা বাস্তব মিলিয়ে। নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করতে শেখে।
সকল শিল্পকলার মধ্যে কতকগুলি মূল বস্তু থাকে যেমন—বিন্দু, রেখা, রং, আকার, গতি বা ছন্দ, আলোছায়া গাঢ়-হালকার সম্পর্ক ইত্যাদি। এই সকলের মিলনেই হয় ছবি বা ভাস্কর্য। আর আছে মাধ্যম, অর্থাৎ কোন মাধ্যমে শিল্পসৃষ্টি হয়েছে। চিত্রকলার মাধ্যম হলো কালি-কলম, জল রং, প্যাস্টেল রং, তেল মিশ্রিত রং ইত্যাদি। ছোটদের জন্য প্যাস্টেল ও জল রং ব্যবহার করা সহজ হয়। বাংলাদেশে পুরাকালে জল রং দিয়েই ছবি আঁকত শিল্পীরা। পুরাতন পুঁথিতে তালপাতায় আঁকা ছবির বহু নিদর্শন আছে। বর্তমানেও জল রং অত্যন্ত প্রিয়, তবে এখন আর কেউ তালপাতায় আঁকে না, কাগজে আঁকে।
ভাস্কর্য। নরম মাটি দিয়ে কোনো কিছুর রূপ দেয়া বা শক্ত পাথর কেটে কোনো গড়ন বানানো। বিশেষ এক ধরনের ছাঁচ বানিয়ে গলিত মেটাল ঢেলে গড়ন বানানো, এই ধরনের কাজকে বলে ভাস্কর্য। আমাদের দেশে পোড়ামাটির ভাস্কর্য খুব প্রসিদ্ধ ছিল।
আমাদের সংস্কৃতি বা কালচার গড়ে উঠেছে নানান শিল্পকলার কারুকাজ দিয়ে। সকল শিল্পীর একটি দায়িত্ব আছে-দেশের ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করা। বাংলায় একটি কথা আছে—'কালি কলম মন, লেখে তিন জন’—কালি মানে দেশের ঐতিহ্যে হাজার বছর প্রবাহিত কালি, কলম হলো শিল্পসৃষ্টির বর্তমান সরঞ্জাম, আর মন হলো বর্তমান যুগের সঙ্গে ঐতিহ্যের মিল করে নিজেকে প্রকাশ করার মন। একটি দেশকে জানা যায় দেশের মানুষকে জানা যায় তার শিল্পকলা চর্চার ধারা দেখে। শিল্পকলা চর্চা সকলের জন্য অপরিহার্য।
সন্ধ্যের আলো-আঁধারিতে, ২৪শে মে, ২০০১, মিয়ানমারের (বার্মার) সীমান্ত শহর মংডুর পথে নেমে আমার মুখ, চোখ, কান ও হৃদয় অচেনা আবেগে উপচে পড়ল।
মংডু আমাদের টেকনাফের ওপারে। মাঝখানে নাফ নদী। মংডু বার্মার পশ্চিম সীমান্তের শহর। ব্রিটিশ যুগের বহু আগে থেকেই চট্টগ্রামের সঙ্গে তার যোগাযোগ। কখনও ছিন্ন, কখনও নিরবচ্ছিন্ন। পাদরি মেস্ট্রো সেবাস্টিন মানরিক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই পথে আসেন। তারও একশ বছর আগে পর্তুগিজরা চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে। তারা নিজেদের বসতির জায়গাকে ব্যাণ্ডেল বলত। চট্টগ্রামে এখন ব্যাণ্ডেল রোড তাদের স্মৃতি বহন করছে।
সন্ধ্যের আঁধার ঘনিয়ে আসার পর আমরা অভিবাসন ও শুল্ক দফতর থেকে ছাড়া পেয়ে খাঁচা ছাড়া পাখির মতো উড়াল দিলাম। এই পথে আসতে পেরে খুশি হয়েছি, পথে আরাকান পড়বে, আরাকান রাজ্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন রাজধানী ম্রাউক-উ দেখতে পাব। এক সময় আরাকান বার্সা থেকে আলাদা স্বাধীন রাজ্য ছিল। তার পরিধি ছিল উত্তরে ফেনী নদী থেকে আন্দামান সাগরের কাছাকাছি পুরো বঙ্গোপসাগর উপকূল। সেখানে এসে পড়েছি এখন। আরাকান রাজ্যের রাজসভায় দৌলত কাজী, আলাওল সাহিত্যচর্চা করেছেন।
ছেলেবেলা থেকে চট্টগ্রামের পাশে অপরূপ মিয়ানমারের কথা শুনে এসেছি রূপকথার গল্পের মতো, আজ তা বাস্তবে ভেসে উঠল সন্ধ্যের আলোছায়ায়। অন্ধকার প্রায় গাঢ় হয়ে এসেছে। আকাশে মেঘের কোলে শুক্লপক্ষের চাঁদ। আমার হাতে ও কাঁধে ঝোলাঝুলি। শুল্ক অফিসের চৌহদ্দি পেরিয়ে পঞ্চাশ কদম না যেতেই বাঁ দিকে বড় বড় রেস্তোরাঁ, প্রায় জনমানবহীন। ডান দিকে মোড় ঘুরতেই দেখি এক মিয়ানমার কুমারী পানীয়ের পসরা নিয়ে বসেছে। একেবারেই ঝুপড়ি দোকান। কুমারীর দোকানের পাশেই আর একটি সে রকম দোকান। তারপর সামনেই শুরু হয়েছে বাড়িঘর ও দোকান। পথে নেমে পড়েছে তরুণ-তরুণী, মেয়ে-পুরুষ। পথে পথে মিয়ানমারের যুবতি-তরুণী। কলহাস্যে মুখর। বাড়ির সামনে, দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কেউ কেউ যুবক, যুবতি, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ। মিয়ানমারের সবাই লুঙ্গি পরে। মেয়েদের পরনে লুঙ্গি ও ঝলমলে ব্লাউজ জাতীয় জামা বা গেঞ্জি । চুলে ফুল গোঁজা, চিরুনি ও রিবন-ফিতে।
পাশ দিয়ে একটা পাইক্যা চলে যাচ্ছে। তিন চাকার রিকশা, যেমন মোটর বাইকের পাশে আর একটা চাকা লাগিয়ে ক্যারিয়ারে বউ বাচ্চা বসতে পারে, এও প্রায় তেমনি। সারা মিয়ানমারে আমাদের রিকশার বদলে পাইক্যা। স্থানীয় মুসলমানরা এর একচেটিয়া চালক। মংডুর ব্যবসাও প্রায় ওদের দখলে, আর হিন্দুরাও আছে।
ইউনাইটেড হোটেলে পৌঁছলাম, কিন্তু জায়গা হলো না। আগে-ভাগে যারা গেছে তারা জায়গা দখল করে নিয়েছে। প্রায় অনাথের মতো বোঁচকা-কুঁচকি নিয়ে নতুন হোটেলের উদ্দেশে চললাম। আমরা খুঁজে পেতে যে হোটেল পেলাম তার অবস্থা শোচনীয় বললে কম বলা হয়। বেড়ার ঘরের দোতলার মাঝবারান্দায় বসেই টের পেলাম এটা চতুর্থ শ্রেণির হোটেল হতেও পারে। কাঠের মেঝে। কাঠের যেমন-তেমন দেয়াল। বিছানায় গিয়ে পরখ করে দেখি উঁচু-নিচু চষা জমির মতো তোশক। মশারিতে বিচিত্র ও বিপরীতধর্মী নানা রকম উৎকট দুর্গন্ধ। মাথার উপরে পাখা আছে। কিন্তু রাত নয়টার পর তো বিজলি থাকবে না। তখন গ্লাভস পরে হাত ধোয়ার অবস্থা হবে। নিলাম ফ্যান ছাড়া একটি কক্ষ। পরে মনে পড়ল ফ্যান থাকলেই বা কী! আমার তো রাতে ফ্যান সহ্য হয় না। বাতিও থাকবে না রাতে
মাঝবয়সী এক নারী আমাদের প্রায় টেনে নিয়ে গেল তার রয়েল রেস্তোরায়, রাতের খাওয়ার জন্য। ইউনাইটেড হোটেলে যারা উঠেছে তারা নাকি ওদিকে এক মুসলিম রেস্তোরাঁয়, খেয়ে নিচ্ছে। রয়েল রেস্তোরা, মন্দ নয়। সুন্দর ঝকঝকে টেবিল-টুল। বাসন-কোসন ভদ্র। ভাতের দোকান বলেই উঁচু টেবিল ও প্লাস্টিকের টুল। সম্ভবত চীন থেকে আমদানি ওই টুল। সাধারণ বর্মি রেস্তোরাঁয় নিচু টেবিল ও টুল থাকে ।
রেস্তোরাঁর রাখাইন মালকিনের বয়স প্রথমে বুঝতে পারিনি। বলে কী! ওর বড় ছেলে কলেজে পড়ে! কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে রাখাইন আছে। এখন বুঝতে পারলাম আমার দেশের রাখাইনদের কত কম জানি । তাদের খাদ্যাভ্যাস, আচার-আচরণ, ভাষা, সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না। তাহলে কী করে দেশের সব মানুষের সঙ্গে আমার সখ্য নিবিড় হবে।
রান্নাঘর থেকে ছুটে এলো একটি মেয়ে। লুঙ্গি এবং কোমর-ঢাকা ব্লাউজ পরেছে। ওর নাম ঝরনা । চেহারা ও স্বাস্থ্য গরিব ঘরের রোগা-পটকা নারীর মতো।
পোড়া লঙ্কা কচলে নুন-তেল দিয়ে ভর্তা করল। একটা প্লেটে তার সঙ্গে দিল কচি লেবুপাতা। বাহ্ । খাস চট্টগ্রামের খাবার। আসলে এদের থেকে চট্টগ্রামের বড়ুয়ারা এই খাবার নিয়েছে। চাকমা মারমারা ধানি লঙ্কা পুড়ে নুন ও পেঁয়াজ দিয়ে ভর্তা করে। পোড়া বা সেদ্ধ ধানি লঙ্কা কুইজ্যায় বা মাটির হামানদিস্তায় পিষে নেয়। একটা রাত কেটে গেল অখ্যাত বা কুশ্রী হোটেলে।
২৫শে মে, দ্বিতীয় দিন। মহাথেরোর সঙ্গে মংডুর প্রধান সড়ক ধরে চলেছি। বাজার। দুইপাশে বাড়ি, বাড়ির নিচে দোকান। ভেতরের বাড়িগুলো সেগুন কাঠের থাম বা পাকা থামের ওপর। গত রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। ভেজা পথ। গাছপালার পাতা চকচক করছে ধাতব নতুন টাকার মতো। বৃষ্টি শিরীষ, আম, কাঁঠাল, কৃষ্ণচূড়া সবই আমাদের মতো। পদাউকের পাতা লকলক করছে। পদাউকের সোনারঙ ফুল ফোটার এটিই সময়।মিয়ানমারে ওদের নাম সেন্না। মংডুর কিছু গাছ ব্রিটিশ আমলের। ওদের বয়স শতাব্দী বা তারও বেশি । বৃষ্টি
শিরীষ, তেঁতুল এবং একটু কম বয়সী নারকেল গাছ। আছে কাঠগোলাপ ও সোনালু। নারকেল সর্বত্র। বাড়ির সামনের নারকেল গাছটির গোড়ার দিকে মাথা সমান উঁচুতে অর্কিড করেছে। তাতে রঙিন ও সাদা ফুল।
পাইক্যায় বোরকা পরা মহিলা। তার ওপর মাথায় ছাতা। ছবি তুলতে যেতেই ছাতা দিয়ে আড়াল তুলে দিল। হাঁটতে হাঁটতে শহরের পূর্ব দিকে শেউইজার সেতু পার হয়ে গেলাম। নদীর নাম সুধার ডিয়ার। এপারে মংডু, ওপারে সুধার পাড়া। মুসলিম গ্রাম।
সেতুর কাছেই পাঁচ-সাতজন মাছ নিয়ে বসেছে। তরিতরকারি নিয়ে বসেছে কয়েকজন। গ্রামের ছোট্ট বাজার। পাঁচ-ছয়টা বেড়ার দোকান। বুড়ো আঙুলের সমান চিংড়ির কিলো ৪ থেকে ৫শ চ্যা। আমাদের তুলনায় পানির দাম। টাকার হিসাবে ৪০ থেকে ৫০ টাকার মধ্যে। নদীর উজান দিকে বিলে দেখা যাচ্ছে চিংড়ির ঘের। অঢেল মাছ পাওয়া যায় ওখানে। চায়ের দোকান থেকে লোকজন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মংডুতে এখনো প্যান্ট দেখিনি । শুধু আমাদের পরনে প্যান্ট। মহাথেরো চীবর পরেছেন। বর্মিরা সবাই লুঙ্গি পরেছে। অফিস কাছারিতেও লুঙ্গি। গতকাল শুল্ক অফিসের দুজনের প্যান্ট দেখেছি। ওরা পুলিশ। অন্যদের লুঙ্গি। লুঙ্গি, ফুঙ্গি ও প্যাগোডা এই তিন নিয়ে মিয়ানমার। ফুঙ্গি হলো বৌদ্ধ ভিক্ষু। গম (ভালো), ছাম্মান বা সাম্পান, ছা (শাবক), থামি (বর্মি রমণীদের সেলাইবিহীন লুঙ্গি) ইত্যাদি অনেক শব্দ বার্মা ও আরাকান থেকে চট্টগ্রাম হয়ে বাংলা ভাষায় ঢুকেছে
বাসের চালে যাত্রীদের সঙ্গে ফুঙ্গি। পথে ঘাটে ফুঙ্গি। সকালে তারা খালি পায়ে ভিক্ষে করতে বের হন। ভিক্ষে ছাড়া ভিক্ষু বা ফুঙ্গিদের চলবে না। ভিক্ষাই তাদের জীবিকা। ভিক্ষুদের পরিধেয় চীবর সেলাইবিহীন লুঙ্গির মতো। গায়ে আলাদা অন্য এক টুকরো চীবর থাকে। হাত কাটা ও এক কাঁধ কাটা একটা গেঞ্জি থাকে, কোমরে বেল্ট জাতীয় অর্থাৎ সেলাই করা কাপড়ের কোমর বন্ধনী থাকে। এসব মিলে ত্রিচীবর। আর হাতে থাকে ছাবাইক বা ভিক্ষাপাত্র। আদিতে এটি কাঠ বা লোহার হতো। এখন লাক্ষা দিয়ে তৈরি হয়। ভিক্ষুদের চীবর বিশেষ মাপে এবং অনেক জোড়া দিয়ে সেলাই করা হয়। এটি নিয়ম। সাধারণ লাল ও লালের কাছাকাছি রঙে চীবরে রঙ করা হয়। বার্মায় ফুঙ্গিদের অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হয়।
ছেলে-বুড়ো যুবক-যুবতি সবার পরিধানে লুঙ্গি। স্কুলের পোশাকও লুঙ্গি ও জামা বা শার্ট। বর্মি মুসলমান- হিন্দু-বড়ুয়া-খ্রিষ্টান সবার লুঙ্গি। বর্মিরা শার্টটি লুঙ্গির নিচে গুঁজে দেয়। মংডুর মুসলিমরা শার্ট পরে লুঙ্গির বাইরে। বার্মা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে বাংলাদেশে লুঙ্গি প্রবেশ করে। মাত্র একশ বছরের মধ্যে সারা বাংলা হয়ে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত লুঙ্গি চলে গেছে। লুঙ্গি, শার্ট ও বর্মি কোট, মাথায় বর্মি টুপি, পায়ে দুই ফিতের মজবুত স্যাণ্ডেল বর্মিদের জাতীয় পোশাক।
লোকজন আমাদের দেখছে। আমাদের পোশাক ও চাল-চলন ওদের থেকে ভিন্ন। সব দেশের লোক বিদেশিদের চিনতে পারে। সেতু পেরিয়ে ফিরে আসছি। কিছুদূর এসে মূল রাস্তা থেকে ডান দিকে বর্মি পাড়ায় ঢুকে পড়লাম। রাস্তার মোড়ে খালি জায়গায় বড় শিরীষ গাছের নিচে মিয়ানমারের তরুণী নুডলস বিক্রি করছে। ভাসমান দোকান। সকালের টিফিন এ রকম এক দোকানে পুলকসহ খেয়েছি। নুডলস, পোড়া লঙ্কাগুড়ো, তেঁতুলের টক, কলার থোড় ইত্যাদি সবজি দিয়ে স্যুপ, ডিমসেদ্ধ মিশিয়ে খেয়েছি। ডিমের খোসা ফেলে কাঁচি দিয়ে টুকরো টুকরো করে ক্ষিপ্র গতিতে। আমার মোটামুটি ভালোই লেগেছে। সকালের জন্য আদর্শ খাবার বলা যায়। সঙ্গে বিনি পয়সায় দুধ চিনি ছাড়া চা দিয়েছে। দোকানি মাঝবয়সী মহিলা। ইঙ্গিতে, ইংরেজিতে কোনোমতে এক রকম করে কথা হলো। বুঝতে পারছি সারা ভ্রমণ এভাবে অপূর্ণ কথাবার্তা বলতে হবে।
দোকানটির দিকে এগিয়ে গেলাম। মাথার উপর ছত্রাকার শিরীষ গাছের নিচে পলিথিন টাঙিয়ে দিয়েছে। লম্বা বেঞ্চিতে খাবারের বড় বড় ডেকচি। টুল আছে বসার। তরুণী বলল, বিকিকিনি শেষ। নুডলস আছে, কিন্তু মশলাপাতি ও তেঁতুলের ঝোল ফুরিয়ে গেছে। ওখান থেকে একটু এগিয়ে চায়ের দোকানে ঢুকলাম। মালকিন বসে আছে চেয়ারে। রোয়াইংগা মুসলিম বয় আছে দুজন। কিন্তু বিস্কুট বা সে রকম কোনো খাবার নেই। দুধ চিনির চা ও বিনি পয়সার চা আছে। দোকানের ভেতরে আরেক মহিলা চুরুট সিগারেট ও পান বেচতে বসেছে। অন্য মহিলারা আছে রান্নাঘরে। চা বানিয়ে দিচ্ছে। মহিলারা চিরস্বাধীন। দোকানের মালিক তারা। সবই খুব সাধারণ মানের। চা খেয়ে বেরিয়ে এলাম ।
বাংলা সনের প্রথম মাসের নাম বৈশাখ। পয়লা বৈশাখে বাঙালির নববর্ষ উৎসব। নববর্ষ সকল দেশের, সকল জাতিরই আনন্দ উৎসবের দিন। শুধু আনন্দ উচ্ছ্বাসই না, সকল মানুষের জন্য কল্যাণ কামনারও দিন। আমরাও সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি ও কল্যাণের প্রত্যাশা নিয়েই মহা ধুমধামের সঙ্গে আমাদের নববর্ষ উৎসব উদযাপন করি। একে অন্যকে বলি, শুভ নববর্ষ।
বাংলা নববর্ষ এখন আমাদের প্রধান জাতীয় উৎসব। প্রতি বছরই এ উৎসব বিপুল মানুষের অংশগ্রহণে বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে উঠছে। বাংলাদেশে যে এতটা প্রাণের আবেগে এবং গভীর ভালোবাসায় এ উৎসব উদ্যাপিত হয় তার কারণ পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলার বাঙালিকে এ উৎসব পালন করতে দেয়া হয়নি । বলা হয়েছে, এটা পাকিস্তানি আদর্শের পরিপন্থী। সে-বক্তব্য ছিল বাঙালির সংস্কৃতির ওপর এক চরম আঘাত। বাঙালি তার সংস্কৃতির ওপর এ আঘাত সহ্য করেনি। তারা এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল বাঙালির এ উৎসবকে জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণার দাবি জানিয়েছে। কিন্তু সে-দাবি অগ্রাহ্য হয়েছে। ফলে পূর্ববাংলার বাঙালি ফুঁসে উঠেছে। সোচ্চার হয়ে উঠেছে প্রতিবাদে। এভাবেই পূর্ববাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালি জাতিসত্তা গঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় বাংলা নববর্ষ এবং তার উদযাপনের আয়োজন ।
১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলার সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ সরকারকে বিপুলভাবে পরাজিত করে যুক্তফ্রন্টের সরকার গঠিত হলে মুখ্যমন্ত্রী ও বাঙালিদের জনপ্রিয় নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের সরকার বাংলা নববর্ষে ছুটি ঘোষণা করেন এবং দেশবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সেটা ছিল বাঙালির এক তাৎপর্যপূর্ণ বিজয়ের দিন। কিন্তু সে-বিজয় স্থায়ী হয়নি। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দিয়ে এবং সামরিক শাসন জারি করে তা সাময়িকভাবে রুখে দিয়েছে স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার। তবু পূর্ববাংলার বাঙালি পিছু হটেনি । সরকারিভাবে আর নববর্ষ উদযাপিত হয়নি পাকিস্তান আমলে; কিন্তু বেসরকারিভাবে উদ্যাপিত হয়েছে প্রবল আগ্রহ ও গভীরতর উৎসাহ-উদ্দীপনায়। এর মধ্যে সবচেয়ে সুসংগঠিত এবং সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানট (১৯৬১)। ১৯৬৭ সাল থেকে রমনার পাকুড়মূলে ছায়ানট নববর্ষের যে-উৎসব শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় বাধাহীন পরিবেশে এখন তা জনগণের বিপুল আগ্রহ-উদ্দীপনাময় অংশগ্রহণে দেশের সর্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। রাজধানী ঢাকার নববর্ষ উৎসবের দ্বিতীয় প্রধান আকর্ষণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রায় মুখোশ, কার্টুনসহ যে-সব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীকধর্মী চিত্র বহন করা হয় তাতে আবহমান বাঙালিত্বের পরিচয় এবং সমকালীন সমাজ-রাজনীতির সমালোচনাও থাকে।
এবার আমরা বাংলা সন ও নববর্ষ উদযাপনের কথা বলি। বাংলা সনের ইতিহাস এখনো সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতই মনে করেন মুগল সম্রাট আকবর চান্দ্র হিজরি সনের সঙ্গে ভারতবর্ষের সৌর সনের সমন্বয় সাধন করে ১৫৫৬ সাল বা ৯৯২ হিজরিতে বাংলা সন চালু করেন। আধুনিক গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন মহামতি আকবর সর্বভারতীয় যে ইলাহি সন প্রবর্তন করেছিলেন তার ভিত্তিতেই বাংলায় আকবরের কোনো প্রতিনিধি বা মুসলমান সুলতান বা নবাব বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। সেজন্যই একে ‘সন' বা 'সাল' বলে উল্লেখ করা হয়। 'সন' কথাটি আরবি, আর ‘সাল' হলো ফারসি। এখনো সন বা সালই ব্যাপকভাবে চালু। তবে বঙ্গাব্দও বলেন কেউ কেউ ।
বাংলা সন চালু হবার পর নববর্ষ উদযাপনে নানা আনুষ্ঠানিকতা যুক্ত হয়। নবাব এবং জমিদারেরা চালু করেন ‘পুণ্যাহ’ অনুষ্ঠান। পয়লা বৈশাখে প্রজারা নবাব বা জমিদার বাড়িতে আমন্ত্রিত হতেন, তাদের মিষ্টিমুখও করানো হতো। পান-সুপারিরও আয়োজন থাকত। তবে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল খাজনা আদায়। মুর্শিদাবাদের নবাবেরা এ অনুষ্ঠান করতেন। বাংলার জমিদারেরাও করতেন এ অনুষ্ঠান। জমিদারি উঠে যাওয়ায় এ অনুষ্ঠান এখন লুপ্ত হয়েছে।
পয়লা বৈশাখের দ্বিতীয় বৃহৎ অনুষ্ঠান ছিল 'হালখাতা'। এ অনুষ্ঠানটি করতেন ব্যবসায়ীরা। বাংলাদেশ কৃষিপ্ৰধান । তাই ফসলের মৌসুমে ফসল বিক্রির টাকা হাতে না এলে কৃষকসহ প্রায় কেউই নগদ টাকার মুখ খুব একটা দেখতে পেত না। ফলে সারাবছর বাকিতে প্রয়োজনীয় জিনিস না কিনে তাদের উপায় ছিল না। পয়লা বৈশাখের হালখাতা অনুষ্ঠানে তারা দোকানিদের বাকির টাকা মিটিয়ে দিতেন। অন্তত আংশিক পরিশোধ করেও নতুন বছরের খাতা খুলতেন । হালখাতা উপলক্ষে দোকানিরা ঝালর কাটা লাল নীল সবুজ বেগুনি কাগজ দিয়ে দোকান সাজাতেন। ধূপধুনা জ্বালানো হতো। মিষ্টিমুখ করানো হতো গ্রাহক-খরিদ্দারদের। হাসি-ঠাট্টা, গল্পগুজবের মধ্যে বকেয়া আদায় এবং উৎসবের আনন্দ উপভোগ দুই-ই সম্পন্ন হতো। হালখাতাও এখন আর তেমন সাড়ম্বরে উদ্যাপিত হয় না। এখন মানুষের হাতে নগদ পয়সা আছে। বাকিতে বিকিকিনি এখন আর আগের মতো ব্যাপক আকারে হয় না।
বাংলা নববর্ষের আর একটি প্রধান অনুষ্ঠান হলো বৈশাখী মেলা। দেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখের প্রথম দিনে বার্ষিক মেলা বসে। এইসব মেলার অনেকগুলোই বেশ পুরনো। এই মেলাগুলোর মধ্যে খুব প্রাচীন ঠাকুরগাঁ জেলার রানীশংকৈল উপজেলার নেকমরদের মেলা এবং চট্টগ্রামের মহামুনির বুদ্ধপূর্ণিমা মেলা। এক সময়ে এইসব মেলা খুব ধুমধামের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হতো। সে-মেলা এখনো বসে, তবে আগের সে জৌলুস এখন আর নেই। আগে গ্রামবাংলার এই বার্ষিক মেলাগুলোর গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। কারণ তখনো সারাদেশে বিস্তৃত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ফলে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল স্থবির। এখন যেমন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে এক দিনের বেশি লাগে না। আগে তা সম্ভব ছিল না। নৌকা, ঘোড়ার গাড়ি, গরুর, মোষের গাড়িতে মানুষ বা পণ্য পরিবহনে বহুসময় বা কয়েকদিন লেগে যেত। এখন নতুন নতুন পাকা রাস্তা ও দ্রুতগতির যানবাহন চালু হওয়ায় সে-সমস্যা আর নেই। আগে এইসব আঞ্চলিক মেলা থেকেই মানুষ সারা বছরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে রাখত। তাছাড়া এইসব মেলা অঞ্চলবিশেষের মানুষের মিলন মেলায়ও পরিণত হতো। নানা সংবাদ আদান-প্রদান, নানা বিষয়ে মত বিনিময়েরও আদর্শ স্থান ছিল এই সব মেলা। আবার বাৎসরিক বিনোদনের জায়গাও ছিল মেলা। মেলায় থাকত কবিগান, কীর্তন, যাত্রা, গম্ভীরা গান, পুতুল নাচ, নাগরদোলাসহ নানা আনন্দ-আয়োজন।
নববর্ষের ওই তিনটি প্রধান সর্বজনীন উৎসব ছাড়াও বহু আঞ্চলিক উৎসব আছে। এদের মধ্যে চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত বলী খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯০৭ সাল থেকে কক্সবাজারসহ বৃহত্তর চট্টগ্রামের নানাস্থানে এই খেলার প্রচলন আছে। এই বিখ্যাত কুস্তি খেলাকেই বলা হয় বলী খেলা। আবদুল জব্বার নামে এক ব্যক্তি এ খেলার প্রবর্তন করেন বলে একে 'জব্বারের বলী খেলা' বলা হয় ।
আমানিও নববর্ষের একটি প্রাচীন আঞ্চলিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। এটি প্রধানত কৃষকের পারিবারিক অনুষ্ঠান। চৈত্র মাসের শেষদিনের সন্ধ্যারাতে গৃহকর্ত্রী এক হাঁড়ি পানিতে স্বল্প পরিমাণ অপক্ব চাল ছেড়ে দিয়ে সারারাত ভিজতে দেন এবং তার মধ্যে একটি কচি আমের পাতাযুক্ত ডাল বসিয়ে রাখেন। পয়লা বৈশাখের সূর্য ওঠার আগে ঘর ঝাড়ু দিয়ে গৃহকর্ত্রী সেই হাঁড়ির পানি সারা ঘরে ছিটিয়ে দেন। পরে সেই ভেজা চাল সকলকে খেতে দিয়ে আমের ডালের কচি পাতা হাঁড়ির পানিতে ভিজিয়ে বাড়ির সকলের গায়ে ছিটিয়ে দেন। তাদের বিশ্বাস, এতে বাড়ির সকলের কল্যাণ হবে। নতুন বছর হবে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির। এ অনুষ্ঠান এখন খুব একটা দেখা যায় না।
নববর্ষের এ ধরনের আরও নানা অনুষ্ঠান আছে। তোমরা নিজ নিজ এলাকায় খোঁজ নিলে তার সন্ধান পাবে। তোমাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে নানা ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায়ও নববর্ষের উৎসব হয়। নানা আনন্দময় ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্য দিয়ে এরা বৈসুব, সাংগ্রাই ও বিজু তিনটিকে একত্র করে 'বৈসাবী' নামে উৎসব করে। গ্রাম-বাংলায় নববর্ষে নানা খেলাধুলারও আয়োজন করা হতো। মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জে হতো গরুর দৌড়, হা-ডু-ডু খেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মোরগের লড়াই, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, নড়াইলে ষাঁড়ের লড়াই প্রভৃতি ।
আমাদের নববর্ষ উৎসব '৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের পর নতুন গুরুত্ব ও তাৎপর্য লাভ করে। আগে সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের আয়োজনের কথা বলেছি। এছাড়া বাংলা একাডেমিতে বৈশাখী ও কারুপণ্য মেলা এবং গোটা বিশ্ববিদ্যালয় ও রমনা এলাকা পয়লা বৈশাখের দিনে লক্ষ মানুষের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে। নতুন পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ছেলেরা এবং নানা রঙের শাড়ি পরে নারীরা এই অনুষ্ঠানকে বর্ণিল করে তোলে। রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলের গান, লোকসংগীত এবং বাঁশির সুরে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে সমবেত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা । আনন্দময় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ এই পরিবেশ আধুনিক বাঙালি জীবনের এক গৌরবময় বিষয়।
কোথা থেকে এসেছে আমাদের বাংলা ভাষা? ভাষা কি জন্ম নেয় মানুষের মতো? বা যেমন বীজ থেকে গাছ জন্মে তেমনভাবে জন্ম নেয় ভাষা? না, ভাষা মানুষ বা তরুর মতো জন্ম নেয় না। বাংলা ভাষাও মানুষ বা তরুর মতো জন্ম নেয়নি, কোনো কল্পিত স্বর্গ থেকেও আসেনি। এখন আমরা যে বাংলা ভাষা বলি, এক হাজার বছর আগে তা ঠিক এমন ছিল না। এক হাজার বছর পরও ঠিক এমন থাকবে না। ভাষার ধর্মই বদলে যাওয়া । বাংলা ভাষার আগেও এদেশে ভাষা ছিল। সে ভাষায় এদেশের মানুষ কথা বলত, গান গাইত, কবিতা বানাত । মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি। রূপ বদলে যায় শব্দের, বদল ঘটে অর্থের। অনেকদিন কেটে গেলে মনে হয় ভাষাটি একটি নতুন ভাষা হয়ে উঠেছে। আর সে ভাষার বদল ঘটেই জন্ম হয়েছে বাংলা ভাষার আজ থেকে একশ বছর আগেও কারও কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে। কেউ জানত না কত বয়স এ ভাষার। সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয় বাংলা ভাষায়। এক দল লোক মনে করতেন ওই সংস্কৃত ভাষাই বাংলার জননী। বাংলা সংস্কৃতের মেয়ে। তবে দুষ্টু মেয়ে, যে মায়ের কথা মতো চলেনি। না চলে চলে অন্য রকম হয়ে গেছে। তবে উনিশ শতকেই আরেক দল লোক ছিলেন, যাঁরা মনে করতেন বাংলার সাথে সংস্কৃতের সম্পর্ক বেশ দূরের। তাঁদের মতে, বাংলা ঠিক সংস্কৃতের কন্যা নয়। অর্থাৎ সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপত্তি ঘটেনি বাংলার। ঘটেছে অন্য কোনো ভাষা থেকে। সংস্কৃত ছিল সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষের লেখার ভাষা। তা কণ্ঠ্য ছিল না। কথা বলত মানুষেরা নানা রকম 'প্রাকৃত' ভাষায় ৷ প্রাকৃত ভাষা হচ্ছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথ্য ভাষা। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, সংস্কৃত থেকে নয়, প্রাকৃত ভাষা থেকেই উদ্ভব ঘটেছে বাংলা ভাষার ।
কিন্তু নানা রকম প্রাকৃত ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে। তাহলে কোন প্রাকৃত থেকে উদ্ভব ঘটেছিল বাংলার? এ সম্পর্কে প্রথম স্পষ্ট মত প্রকাশ করেন জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন। বহু প্রাকৃতের একটির নাম মাগধী প্রাকৃত। তাঁর মতে মাগধী প্রাকৃতের কোনো পূর্বাঞ্চলীয় রূপ থেকে জন্ম নেয় বাংলা ভাষা। পরে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আমাদের চোখে স্পষ্ট ধরা দেয় বাংলা ভাষার ইতিহাস। যে ইতিহাস বলার জন্য আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে। পিছিয়ে যেতে হবে অন্তত কয়েক হাজার বছর।
ইউরোপ ও এশিয়ার বেশ কিছু ভাষার ধ্বনিতে, শব্দে লক্ষ করা যায় গভীর মিল। এ ভাষাগুলো যে সব অঞ্চলে ছিল ও এখন আছে, তার সবচেয়ে পশ্চিমে ইউরোপ আর সবচেয়ে পূর্বে ভারত ও বাংলাদেশ। ভাষাতাত্ত্বিকেরা এ ভাষাগুলোকে একটি ভাষাবংশের সদস্য বলে মনে করেন। ওই ভাষাবংশটির নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ বা ভারতী-ইউরোপীয় ভাষাবংশ। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশে আছে অনেকগুলো ভাষা-শাখা, যার একটি হচ্ছে ভারতীয় আর্যভাষা । ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন ভাষাগুলোকে বলা হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন রূপ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলোতে। এগুলো সম্ভবত লিখিত হয়েছিল যিশুখ্রিষ্টের জন্মেরও এক হাজার বছর আগে, অর্থাৎ ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। বেদের শ্লোকগুলো পবিত্র বিবেচনা করে তার অনুসারীরা সেগুলো মুখস্থ করে রাখত। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে যেতে থাকে। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা ব্যবহার করত বদলে যেতে থাকে সে ভাষা। এক সময় সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে বেদের ভাষা বা বৈদিক ভাষা। তখন ব্যাকরণবিদরা নানা নিয়ম বিধিবদ্ধ করে একটি মানসম্পন্ন ভাষা সৃষ্টি করেন। এই ভাষার নাম ‘সংস্কৃত’, অর্থাৎ বিধিবদ্ধ, পরিশীলিত, শুদ্ধ ভাষা। খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দের আগেই এ ভাষা বিধিবদ্ধ হয়েছিল।
যিশুর জন্মের আগেই পাওয়া যায় ভারতীয় আর্য-ভাষার তিনটি স্তর। প্রথম স্তরটির নাম বৈদিক বা বৈদিক সংস্কৃত । খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ অব্দ এ ভাষার কাল। তারপর পাওয়া যায় সংস্কৃত। খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ অব্দের দিকে এটি সম্ভবত বিধিবদ্ধ হতে থাকে এবং খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দের দিকে ব্যাকরণবিদ পাণিনির হাতেই এটি চূড়ান্তভাবে বিধিবদ্ধ হয়। বৈদিক ও সংস্কৃতকে বলা হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। প্রাকৃত ভাষাগুলোকে বলা হয় মধ্যভারতীয় আর্যভাষা। মোটামুটিভাবে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দ থেকে ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ ভাষাগুলো কথ্য ও লিখিত ভাষারূপে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত থাকে। এ প্রাকৃত ভাষাগুলোর শেষ স্তরের নাম অপভ্রংশ অর্থাৎ যা খুব বিকৃত হয়ে গেছে। বিভিন্ন অপভ্রংশ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে নানান আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা- বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, পাঞ্জাবি প্রভৃতি ভাষা ।
ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, পূর্ব মাগধী অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে বাংলা; আর আসামি ও ওড়িয়া ভাষা। তাই বাংলার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আসামি ও ওড়িয়ার। আর কয়েকটি ভাষার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা রয়েছে বাংলার সঙ্গে; কেননা সেগুলোও জন্মেছিল মাগধী অপভ্রংশের অন্য দুটি শাখা থেকে। ওই ভাষাগুলো হচ্ছে মৈথিলি,মাগধি, ভোজপুরিয়া। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে অবশ্য একটু ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি একটি প্রাকৃতের নাম বলেন গৌড়ী প্রাকৃত। তিনি মনে করেন, গৌড়ী প্রাকৃতেরই পরিণত অবস্থা গৌড়ী অপভ্রংশ থেকে উৎপত্তি ঘটে বাংলা ভাষার ।
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Maiores ipsum repellat minus nihil. Labore, delectus, nam dignissimos ea repudiandae minima voluptatum magni pariatur possimus quia accusamus harum facilis corporis animi nisi. Enim, pariatur, impedit quia repellat harum ipsam laboriosam voluptas dicta illum nisi obcaecati reprehenderit quis placeat recusandae tenetur aperiam.
সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে।
লালন কয়, জেতের কী রূপ, দেখলাম না এ নজরে ॥
কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়,
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে ॥
গর্তে গেলে কূপজল কয়,
গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়,
মূলে এক ভাল, সে যে ভিন্ন নয়,
ভিন্ন জানায় পাত্র-অনুসারে ॥
জগৎ বেড়ে জেতের কথা,
লোকে গৌরব করে যথা তথা,
লালন সে জেতের ফাতা
বিকিয়েছে সাধ বাজারে।
রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো। তব মনঃকোকনদে।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত-হ্রদে।
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন
কিন্তু কোন গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে।
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে! !
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরসকী বসন্ত, কী শরদে
শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই আর সবই গেছে ঋণে।
বাবু বলিলেন,'বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।'
কহিলাম আমি, তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই।
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়ো-জোর মরিবার মতো ঠাঁই।'
শুনি রাজা কহে, “বাপু, জানো তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা—
ওটা দিতে হবে।' কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া
পাপি সজল চক্ষে,‘করুন রক্ষে গরিবের ভিটেখানি।
সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!”
আঁখি করি লাল রাজা ক্ষণকাল রহিল মৌনভাবে,
কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে।
পরে মাস দেড়ে ভিটে মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে—
করিল ডিক্রি, সকলই বিক্রি মিথ্যা দেনার খতে।
এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি-
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।
মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহগর্তে,
তাই লিখি দিল বিশ্বনিখিল দু বিঘার পরিবর্তে।
সন্ন্যাসীবেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য!
ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি
তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারি নে সেই দুই বিঘা জমি।
হাটে মাঠে বাটে এই মতো কাটে বছর পনেরো-ষোলো—
একদিন শেষে ফিরিবারে দেশে বড়োই বাসনা হলো।
নমোনমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ,
স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল-নিশীথশীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে-
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।
দুই দিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে—
কুমোরের বাড়ি দক্ষিণে ছাড়ি রথতলা করি বামে,
রাখি হাটখোলা, নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে
তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে।
ধিক ধিক ওরে, শত ধিক তোরে,নিলাজ কুলটা ভূমি!
যখনি যাহার তখনি তাহার, এই কী জননী তুমি!
সে কি মনে হবে একদিন যবে ছিলে দরিদ্রমাতা
আঁচল ভরিয়া রাখিতে ধরিয়া ফল ফুল শাক পাতা!
আজ কোন রীতে কারে ভুলাইতে ধরেছ বিলাসবেশ—
পাঁচরঙা পাতা অঞ্চলে গাঁথা, পুষ্পে খচিত কেশ!
আমি তোর লাগি ফিরেছি বিবাগি গৃহহারা সুখহীন—
তুই হেথা বসি ওরে রাক্ষসী, হাসিয়া কাটাস দিন!
ধনীর আদরে গরব না ধরে! এতই হয়েছ ভিন্ন
কোনোখানে লেশ নাহি অবশেষ সেদিনের কোনো চিহ্ন!
কল্যাণময়ী ছিলে তুমি অয়ি, ক্ষুধাহরা সুধারাশি!
যত হাসো আজ যত করো সাজ ছিলে দেবী, হলে দাসী।
বিদীর্ণ-হিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারি দিকে চেয়ে দেখি—
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে, সেই আমগাছ, এ কি!
বসি তার তলে নয়নের জলে শান্ত হইল ব্যথা,
একে একে মনে উদিল স্মরণে বালক-কালের কথা।
সেই মনে পড়ে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে রাত্রে নাহিকো ঘুম,
অতি ভোরে উঠি তাড়াতাড়ি ছুটি আম কুড়াবার ধুম।
সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা পলায়ন—
ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন!
সহসা বাতাস ফেলি গেল শ্বাস শাখা দুলাইয়া গাছে,
দুটি পাকা ফল লভিল ভূতল আমার কোলের কাছে।
ভাবিলাম মনে বুঝি এতখনে আমারে চিনিল মাতা,
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা।
হেনকালে হায় যমদূত প্রায় কোথা হতে এল মালি,
ঝুঁটি-বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি।
কহিলাম তবে, ‘আমি তো নীরবে দিয়েছি আমার সব-
দুটি ফল তার করি অধিকার, এত তারি কলরব!'
চিনিল না মোরে, নিয়ে গেল ধরে কাঁধে তুলি লাঠিগাছ
বাবু ছিপ হাতে পারিষদ সাথে ধরিতেছিলেন মাছ।
শুনি বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, ‘মারিয়া করিব খুন।'
বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ।
আমি কহিলাম,‘শুধু দুটি আম ভিখ মাগি মহাশয়!”
বাবু কহে হেসে ‘বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।’
আমি শুনে হাসি আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে—
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে!
করিতে পারি না কাজ,
সদা ভয়, সদা লাজ,
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।
আড়ালে আড়ালে থাকি,
নীরবে আপনা ঢাকি,
সম্মুখে চরণ নাহি চলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।
হৃদয়ে বুদবুদ মতো
উঠে শুভ্র চিন্তা কত,
মিশে যায় হৃদয়ের তলে
পাছে লোকে কিছু বলে।
কাঁদে প্রাণ যবে, আঁখি
সযতনে শুষ্ক রাখি
নির্মল নয়নের জলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।
একটি স্নেহের কথা
প্রশমিতে পারে ব্যথা
চলে যাই উপেক্ষার ছলে
পাছে লোকে কিছু বলে।
মহৎ উদ্দেশ্যে যবে
এক সাথে মিলে সবে,
পারি না মিলিতে সেই দলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।
বিধাতা দিছেন প্রাণ
থাকি সদা ম্রিয়মাণ;
শক্তি মরে ভীতির কবলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।
বিভো, দেহ হৃদে বল!
না জানি ভকতি, নাহি জানি স্তুতি,
কী দিয়া করিব, তোমার আরতি
আমি নিঃসম্বল!
তোমার দুয়ারে আজি রিক্ত করে
দাঁড়ায়েছি প্রভো, সঁপিতে তোমারে
শুধু আঁখি জল,
দেহ হৃদে বল!
বিভো, দেহ হৃদে বল!
দারিদ্র্য পেষণে, বিপদের ক্রোড়ে,
অথবা সম্পদে, সুখের সাগরে
ভুলি নি তোমারে এক পল,
জীবনে মরণে, শয়নে স্বপনে
তুমি মোর পথের সম্বল;
দেহ হৃদে বল!
বিভো, দেহ হৃদে বল!
কত জাতি পাখি, নিকুঞ্জ বিতানে
সদা আত্মহারা তব গুণগানে,
আনন্দে বিহ্বল!
ভুলিতে তোমারে, প্রাণে অবসাদ,
তরুলতা শিরে, তোমারি প্রসাদ
চারু ফুল ফল!
দেহ হৃদে বল!
বিভো, দেহ হৃদে বল!
তোমারি নিঃশ্বাস বসন্তের বায়ু,
তব স্নেহ কণা জগতের আয়ু,
তব নামে অশেষ মঙ্গল!
গভীর বিষাদে, বিপদের ক্রোড়ে,
একাগ্র হৃদয়ে স্মরিলে তোমারে
নিভে শোকানল।
দেহ হৃদে বল!
(সংক্ষেপিত)
পানিপথে হত। দখল করিয়া দিল্লির শাহিগদি,
দেখিল বাবুর এ-জয় তাঁহার ফাঁকি,
ভারত যাদের তাদেরি জিনিতে এখনো রয়েছে বাকি।
গর্জিয়া উঠিল সংগ্রাম সিং, ‘জিনেছ মুসলমান,
জয়ী বলিব না এ দেহে রহিতে প্রাণ ।
লয়ে লুণ্ঠিত ধন
দেশে ফিরে যাও, নতুবা মুঘল, রাজপুতে দাও রণ।'
খানুয়ার প্রান্তরে
সেই সিংহেরো পতন হইল বীর বাবুরের করে।
এ বিজয় তার স্বপ্ন-অতীত, যেন বা দৈব বলে
সারা উত্তর ভারত আসিল বিজয়ীর করতলে।
কবরে শায়িত কৃতঘ্ন দৌলত,
বাবুরের আর নাই কোনো প্রতিরোধ।
দস্যুর মতো তুষ্ট না হয়ে লুণ্ঠিত সম্পদে,
জাঁকিয়া বসেছে মুঘল সিংহ দিল্লির মসনদে।
মাটির দখলই খাঁটি জয় নয় বুঝেছে বিজয়ী বীর,
বিজিতের হৃদি দখল করিবে এখন করেছে স্থির।
প্রজারঞ্জনে বাবুর দিয়াছে মন,
হিন্দুর-হৃদি জিনিবার লাগি করিতেছে সুশাসন,
ধরিয়া ছদ্মবেশ
ঘুরি পথে পথে খুঁজিয়ে প্রজার কোথায় দুঃখ ক্লেশ।
চিতোরের এক তরুণ যোদ্ধা রণবীর চৌহান
করিতেছে আজি বাবুরের সন্ধান,
কুর্তার তলে কৃপাণ লুকায়ে ঘুরিছে সে পথে পথে
দেখা যদি তার পায় আজি কোনো মতে
লইবে তাহার প্রাণ,
শোণিতে তাহার ক্ষালিত করিবে চিতোরের অপমান।
দাঁড়ায়ে যুবক দিল্লির পথ-পাশে
লক্ষ করিছে জনতার মাঝে কেবা যায় কেবা আসে।
হেন কালে এক মত্ত হস্তী ছুটিল পথের পরে
পথ ছাড়ি সবে পলাইয়া গেল ডরে।
সকলেই গেল সরি
কেবল একটি শিশু রাজপথে রহিল ধুলায় পড়ি।
হাতির পায়ের চাপে
'গেল গেল' বলি হায় হায় করি পথিকেরা ভয়ে কাঁপে।
‘কুড়াইয়া আন ওরে’
সকলেই বলে অথচ কেহ না আগায় সাহস করে।
সহসা একটি বিদেশি পুরুষ ভিড় ঠেলে যায় ছুটে,
‘কর কী কর কী” বলিয়া জনতা চিৎকার করি উঠে।
করি-শুণ্ডের ঘর্ষণ দেহে সহি
পথের শিশুরে কুড়ায়ে বক্ষে বহি
ফিরিয়া আসিল বীর।
চারি পাশে তার জমিল লোকের ভিড়।
বলিয়া উঠিল এক জন, 'আরে এ যে মেথরের ছেলে,
ইহার জন্য বে-আকুফ তুমি তাজা প্রাণ দিতে গেলে?
খুদার দয়ায় পেয়েছ নিজের জান,
ফেলে দিয়ে ওরে এখন করগে স্নান।'
শিশুর জননী ছেলে ফিরে পেয়ে বুকে
বক্ষে চাপিয়া চুমু দেয় তার মুখে।
বিদেশি পুরুষে রাজপুত বীর চিনিল নিকটে এসে,
এ যে বাদশাহ স্বয়ং বাবুর পর্যটকের বেশে।
ভাবিতে লাগিল, 'হরিতে ইহারই প্রাণ
পথে পথে আমি করিতেছি সন্ধান?
বাবুরের পায়ে পড়ি সে তখন লুটে
কহিল সঁপিয়া গুপ্ত কৃপাণ বাবুরের করপুটে,”
‘জাঁহাপনা, এই ছুরিখানা দিয়ে আপনার প্রাণবধ
করিতে আসিয়া একি দেখিলাম! ভারতের রাজপদ
সাজে আপনারে, অন্য কারেও নয়।
বীরভোগ্যা এ বসুধা এ কথা সবাই কয়,
ভারত-ভূমির যোগ্য পালক যেবা,
তাহারে ছাড়িয়া, এ ভূমি অন্য কাহারে করিবে সেবা?
কেটেছে আমার প্রতিহিংসার অন্ধ মোহের ঘোর,
সঁপিনু জীবন, করুন এখন দণ্ডবিধান মোর।'
রাজপথ হতে উঠায়ে যুবকটিরে
কহিল বাবুর ধীরে,
‘বড়ই কঠিন জীবন দেওয়া যে জীবন নেওয়ার চেয়ে;
জান না কি ভাই? ধন্য হলাম আজিকে তোমারে পেয়ে
আজি হতে মোর শরীর রক্ষী হও;
প্রাণ-রক্ষকই হইলে আমার, প্রাণের ঘাতক নও।'
সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান
মাতা ভগ্নি ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোনো কালে একা হয় নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী।
সে-যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না কো, নারীরা আছিল দাসী।
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি৷
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে
যুগের ধর্ম এই—
পীড়ন করিলে সে-পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।
[সংক্ষেপিত]
আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে- এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়— হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হবো— কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমির গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়,
হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে,
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে,
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়; – রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে –
এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে লম্বা মাথার চুল,
কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কিসের রঙিন ফুল!
কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি-মুখের মায়া,
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।
জালি লাউয়ের ডগার মতো বাহু দুখান সরু,
গা খানি তার শাওন মাসের যেমন তমাল তরু।
বাদল-ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজলি মেয়ে পিছলে পড়ে ছড়িয়ে আলোর খেল।
কচি ধানের তুলতে চারা হয়তো কোনো চাষি,
মুখে তাহার জড়িয়ে গেছে কতকটা তার হাসি।
কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দতের কালি দিয়েই কেতাব কোরান লেখি।
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়;
চাষিদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়।
সোনায় যে-জন সোনা বানায়, কিসের গরব তার
রং পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার।
কালোয় যে-জন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন,
তারির পদ-রজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন।
সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ
কালো-বরন চাষির ছেলে জুড়ায় যেন বুক।
যে কালো তার মাঠের ধান, যে কালো তার গাঁও!
সেই কালোতে সিনান করি উজল তাহার গাও।
আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানাটানি।
জারির গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
শাল-সুন্দি-বেত' যেন ও, সকল কাজেই লাগে।
বুড়োরা কয়, ছেলে নয় ও, পাগাল লোহা যেন,
রূপাই যেমন বাপের বেটা কেউ দেখেছ হেন?
যদিও রূপা নয়কো রুপাই, রূপার চেয়ে দামি,
এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামি।
মৌসুমি ফুলের গান মোর কণ্ঠে জাগে নাকো আর
চারিদিকে শুনি হাহাকার ।
ফুলের ফসল নেই, নেই কারও কণ্ঠে আর গান
ক্ষুধার্ত ভয়ার্ত দৃষ্টি প্রাণহীন সব মুখ স্নান ।
মাটি অরণ্যের পানে চায়
সেখানে ক্ষরিছে স্নেহ পল্লবের নিবিড় ছায়ায়।
জাগো তবে অরণ্য কন্যারা। জাগো আজি,
মর্মরে মর্মরে ওঠে বাজি
বৃক্ষের বক্ষের বহ্নিজ্বালা
মেলি লেলিহান শিখা তোমরা জাগিয়া ওঠো বালা!
কঙ্কণে তুলিয়া ছন্দ তান
জাগাও মুমূর্ষু ধরা-প্রাণ
ফুলের ফসল আনো, খাদ্য আনো ক্ষুধার্তের লাগি
আত্মার আনন্দ আনো, আনো যারা রহিয়াছে জাগি
তিমির প্রহর ভরি অতন্দ্র নয়ন, তার তরে
ছড়াও প্রভাত আলো তোমাদের মুঠি ভরে ভরে।
হে সূর্য। শীতের সূর্য।
হিমশীতল সুদীর্ঘ রাত তোমার প্রতীক্ষায়
আমরা থাকি,
যেমন প্রতীক্ষা করে থাকে কৃষকের চঞ্চল চোখ
ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলির জন্যে।
হে সূর্য, তুমি তো জানো,
আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব!
সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে,
এক টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে,
কত কষ্টে আমরা শীত আটকাই।
সকালের এক টুকরো রোদ্দুর-
এক টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামি।
ঘর ছেড়ে আমরা এদিক-ওদিকে যাই—
এক টুকরো রোদ্দুরের তৃষ্ণায়।
হে সূর্য!
তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও,
আর উত্তাপ দিও
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
হে সূর্য।
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও—
শুনেছি, তুমি এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড,
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই
এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হব।
তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা,
তখন হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারব
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।
আজ কিন্তু আমরা তোমার অকৃপণ উত্তাপের প্রার্থী
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অঙ্গ-গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি
জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কালবোশেখিরা
শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি
দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, না, খুন-রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি ॥
সেদিনও এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে;
পথে পথে ফোটে রজনিগন্ধা অলকানন্দা যেন,
এমন সময় ঝড় এলো এক, ঝড় এলো ক্ষ্যাপা বুনো॥
সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি ॥
তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী
আমার শহিদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালব ফেব্রুয়ারি
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি ॥
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Maiores ipsum repellat minus nihil. Labore, delectus, nam dignissimos ea repudiandae minima voluptatum magni pariatur possimus quia accusamus harum facilis corporis animi nisi. Enim, pariatur, impedit quia repellat harum ipsam laboriosam voluptas dicta illum nisi obcaecati reprehenderit quis placeat recusandae tenetur aperiam.